ছোটোবেলা বিশেষ সংখ্যা - ৯৯
সম্পাদকীয়,
রাত পোহালেই শিক্ষক দিবস। দু বছর পর এবার তোমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই দিনটি পালন করবে বলে তোরজোড় করছো জানি। ঐ দেখ, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পর ছেলেদুটো আলোচনা করছে স্যারকে শিক্ষক দিবসে কি উপহার দেওয়া যায় তাই নিয়ে। আমাকে কে বলল? কেন কল্যাণ আঙ্কেল ছবি তুলে পাঠালো যখন তখনই তো বলল। এদিকে যে সন্ধে হয়ে আসছে, বাড়িতে মা চিন্তা করবে তার কোনো খেয়াল আছে ছেলেদুটোর? মা মাত্রই চিন্তা করে। এই যে জয়াবতী অন্য গাঁয়ে বিদ্যা অর্জন করতে গেছে, তারজন্য ওর মা সবসময় চিন্তা করে তা কি তোমরা জানো? জানবে কি করে? আজকে জয়াবতীর জয়যাত্রা পড়লে তবেই না জানবে।আজকের ছোটোবেলা পড়লে আর যেটা জানবে তাহল, গায়ক পাখিদের কথা। শ্রীছন্দা পিসি কত কি জানেন তাই ভেবে আমি তো অবাক। এদিকে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসছে সেটা খেয়াল করেছো কি? তারমানে শরৎকাল এসে গেছে। শরৎকাল নিয়ে ছড়া লিখে পাঠিয়েছেন শ্রাবণী পিসি। শরৎকাল বলতেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। ওনার কথা লিখেছেন পীযূষ আঙ্কেল। আর শরৎকাল মানেই উৎসব। উৎসব মানেই উৎসব সংখ্যা। এই উৎসব সংখ্যার জন্য তোমরা সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়ে দাও। আরেবাবা, স্যার ম্যামদের শিক্ষক দিবসে ছবি এঁকে দাও। আর দেবার আগে খিচিক করে একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও ছোটোবেলার দপ্তরে। স্যার ম্যামরাও খুশি, ছোটোবেলার বন্ধুরাও খুশি। তাই না? --- মৌসুমী ঘোষ।
ধারাবাহিক উপন্যাস
জয়াবতীর জয়যাত্রা
৩১ প র্ব
তৃষ্ণা বসাক
৩৫
পিতাঠাকুর তাঁর টোলের ছাত্রদের ছুটি দিয়েছিলেন একটু আগে আগেই। ইচ্ছে ছিল এখন মেয়ের সঙ্গে বসে দুটো কথা কইবেন। নতুন দেশ কেমন লাগছে, পড়ালেখা কেমন লাগছে, কী কী নতুন বিদ্যা শিখল মেয়ে, এইসব শেখা তার চিন্তাজগতকে কেমনভাবে পালটে দিচ্ছে-এইসব নিয়ে একটু কথা কইবেন। এই কয়েকমাস এইসব প্রশ্নই তাঁর মাথায় ঘুরছে। জয়াবতীর মা মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করত খুব, কিন্তু সে ভাবত মেয়ে কী খাচ্ছে, পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেল কিনা, গাছ থেকে পড়ে পা হাত ভাঙল কিনা এইসব। চিন্তা করলেও সারাদিনের সংসারের খাটনি, তারপর দুরন্ত ছেলে দুর্গাগতিকে সামলানো- সে দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়ত শয্যায় পিঠ ঠেকলেই। ঘুমোতে পারতেন না রামগতি। তিনি কেবল ছটফট করতেন। ভাবতেন দেশাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে মেয়েকে তো বিদ্যাশিক্ষা করতে পাঠালেন, সে মেয়ে কেমন ভাবে নিতে পারে এই নতুন ঢেউ। শিব গড়তে বাঁদর হয়। হয়তো বিদ্যাশিক্ষা করল, কিন্তু উদ্ধত অমানুষ হয়ে গেল। উৎসকে অস্বীকার করল শিক্ষার দর্পে। কিন্তু জয়াবতী আসার পর থেকে যেটুকু দেখলেন, তাতে তাঁর সেসব চিন্তা অমূলক মনে হচ্ছে। মেয়েকে দেখে তাঁর গর্বে দু চোখ ভরে যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করছে মেয়ের চেহারা। পুণ্যির মতো মুখচোরা মেয়েও কত চটপটে হয়ে গেছে। সঙ্গের বাকি দুটি মেয়েকে দেখেও চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দেবী দুর্গা তার সৈন্যদের নিয়ে অসুর দলনে নেমেছে। এখন ভেবেছিলেন মেয়ের সঙ্গে বসে দুটো কথা বলবেন, কিন্তু কোথা থেকে উৎপাতের মতো জমিদারের পালকি এসে হাজির। তিনি খড়ম পায়ে উঠোনে নেমে হারানকে বললেন ‘শোনো হারান, তুমি জমিদার মশাইকে গিয়ে বলো আমার মেয়ে সবে এতটা পথ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, পথশ্রমে ক্লান্ত, আজ নয়, কাল সকালেই যাবে। পালকি তখনি পাঠাতে বলো’
হারান বলল ‘কিন্তু মাঠানের শরীর মোটে ভাল না, পণ্ডিতমশাই, তাই খর খর যেতে হবে’
জয়াবতী কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয়। সবার সামনে সব কথা বলা যায় কি? সে পিতাঠাকুরকে নিচু গলায় বলল ‘নেমন্তন্ন খেতে তো না, একটা মানুষের অসুক শুনে বদ্যি কি না গিয়ে থাকতে পারে? সেনমশাই শিকিয়েচেন, বদ্যির সবসময় কর্তব্য তার রুগীর প্রতি। আর আমি আদৌ ক্লান্ত নই। দিব্যি রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে চলে এসেচি। কোন ক্লান্তি নেই। মন ভাল থাকলে কোন ক্লান্তি আসেনা পিতাঠাকুর। আসলে আমরা সবাই শরীরের চিকিচ্ছে করি, মনের চিকিচ্ছে করলে দেখতেন পিথিমিতে এত রোগ বালাই থাকত না’
মেয়ে তো বরাবরই স্পষ্ট কথা বলত, জেদ খুব, যা করবে ভেবেছে, সেটাই করবে। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন ওর বোধ দেখে। তিনি বারণ করেছেন, তাও যে ওদের যাওয়া দরকার-সে কথাটা সবার সামনে বলল না, পাছে তাঁর অপমান হয়, নিচু গলায় তাঁকে বুঝিয়ে বলল। তাঁর বুক ভরে ওঠে গর্বে। এই বয়সেই এতখানি বিচক্ষণতা যার, সে মেয়ে অনেক বড় হবে।
তিনি আর কোন কথা না বলে ওর মাথায় হাত রাখেন, তারপর ভেতরে চলে যান। পড়ানো শেষ হলে তিনি একটু বিশ্রাম করেন এইসময়। জয়াবতীর মা বলেন ‘জমিদারবাড়ি যাবি, এমনি এমনি কি যাওয়া যায়? কখানা গহনা বার করে দি সিন্দুক থেকে, সবাই ভাগ করে পরে যা, আর রেশমি শাড়ি আছে দুখানা, পুণ্যির মায়ের কি খুড়ির কাছে আরো দুখানা হবে নিশ্চয়, ছুটে গিয়ে চেয়ে আন তো পুণ্যি’
‘গহনা? গহনা কী হবে? রেশমি শাড়িই বা চাইতে যেতে হবে কেন? এই তো দিব্যি নতুন শাড়ি পরেছি’ জয়াবতী অবাক।
জয়াবতীর মা রেগে যান মেয়ের বুদ্ধি দেখে। ‘এই বুদ্ধি নিয়ে তুই বদ্যি হবি? ওরে, জমিদারমশাইয়ের বাড়ি যাচ্ছিস, গিয়ে দেখবি তাঁর বাড়ির মেয়ে বউরা বাড়িতেই সব কত দামি শাড়ি পরে, এক গা গহনা পরে বসে আছে। আর সেখানে তুই এমন ভাবে যাবি? তোর পিতাঠাকুরের মান থাকবে?’
জয়াবতী হেসে ফেলে মার যুক্তি শুনে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে ‘ মা গো মা। পিতাঠাকুরের মান তাঁর বিদ্যায়। আশীর্বাদ কর সেই মান যেন আমরা বজায় রাখতে পারি। তুমি তো ভারি অবাক একটা বললে। রুগী ওদিকে মরতে বসেছে আর বদ্যি গহনা আর রেশমি শাড়ি পরবে বসে বসে, তবে যাবে? শোনো মা, জমিদারমশাইয়ের মায়ের অসুক, তাঁকে দেখার জন্যে আমার ডাক পড়েছে। মানে জয়াবতী বদ্যি যাচ্ছে রুগী দেখতে, তোমার মেয়ে জয়াবতী পূজা কি বে-র নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে না। নেমন্তন্ন খেতে যখন যাব, তখন যত খুশি তোমার গহনায় সাজিও। নে পুণ্যি, ওষুধের পেঁটরাটা নিয়ে আয় দিকি চটপট। আর ভাল কতা মা, জমিদারবাড়ি থেকে ঘুরে এসে তোমাদের শাড়ি ধুতি বার করে দেব।‘
‘কীসের শাড়ি ধুতি আবার?’
‘ঠাকমা পুজোয় সবার জন্য পাটিয়েচে’
‘সে কতা আগে বলতে হয়। আমাকেও তো পাটাতে হবে উলটে ওঁদের সবার জন্যে। নইলে তো তোদের পিতাঠাকুরের নিন্দে হবে‘ জয়াবতীর মার মুখে চিন্তার ছাপ।
‘তুমিও যেমন মা। এসব কি পালিয়ে যাচ্ছে? ভাতৃদ্বিতীয়ার পর যকন যাব, তকন দিও।‘
‘ওঁরা রাগ করবেন না?’
‘দূর ওঁরা তেমন লোকই না’
পেরজাপতি আর উমাশশী বুঝতে পারছিল না তারা কী করবে। যদিও জয়াবতী দুখানা পালকি পাঠাতে বলেছে, কিন্তু জমিদারমশাই ডেকে পাঠিয়েছে তো বদ্যি ঠাকরুনদের, সেখানে তারা কীভাবে?
পেরজাপতি ভাবছিল, কিন্তু বলার সাহস হচ্ছিল না। মুখ খুলল উমাশশীই ‘ ও সাগরজল, হংস মধ্যে বক যথা আমরা গিয়ে কী করব? ‘
‘জেঠামি করিস নি সাগরজল। আমার গাঁয়ে এসে পড়েচ যকন, আমার কথাই শুনতে হবে। ‘ এরপর জয়াবতী বলতে যাচ্ছিল ‘তোর গাঁয়ে যকন যাব তকন তোর কতা শুনে চলব’ সেটা সে সামলে নিল। এখনো উমাশশী বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। কে জানে কী দুঃখ সে মনের মধ্যে পুষে রেকেচে! আজকাল জয়াবতীর মাঝে মধ্যেই সন্দেহ হয় উমাশশীকে সত্যি কি ডাকাতরা তুলে নিয়ে গেছিল নাকি সে কোন কারণে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়ে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল? যাক গে, জোর করে এসব জানা যাবে না, একদিন মন হলে ও নিজেই বলবে। আসলে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁচিয়ে মানুষের মন থেকে বার করার মতো ধৈর্য তার নেই। এ কাজের যোগ্য মেয়ে হচ্ছে পুণ্যি। সে খুব লোকের পেছনে লেগে থেকে ঘ্যানঘ্যান করে সব আদায় করতে পারে। তার আছে এক মোক্ষম অস্ত্র, কান্না, যাতে সবাই ঘায়েল হয়। সেই কান্নাটা ঠিক আসে না জয়াবতীর। মানুষ বুদ্ধি দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে যে কাজ করতে পারে, কেঁদে তা আদায় করার মধ্যে বুদ্ধির অপমান মনে হয় জয়াবতীর। তাতে কি মানুষ নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যায় না? ছিঁচকাঁদুনি স্বভাবের জন্য পুণ্যি তো কম বকুনি খায়নি তার কাছে, তবু ও শোধরাল না, শোধরাবেই না এ জন্মে। নিজেকেই তার জন্যে একটু বদলাতে হচ্ছে জয়াবতীকে। বদলানো মানে নিজে কাঁদুনী হয়ে যাওয়া নয়। বদলানো মানে পুণ্যির এই বিশ্রী স্বভাবটাকে মানুষের কোন ভাল কাজে লাগান যায় সেটা খতিয়ে দেখা। জয়াবতী ঠিক করল উমাশশীর মনের তল পেতে পুণ্যিকেই ওর মনের মধ্যে ডুবুরি নামাতে হবে, সে তো আর সাগরজল এমনি এমনি পাতায় নি, এ তো আর ডোবা, কি পুকুর নয়, এমনকি নদীও নয়, এ হচ্ছে সমুদ্দুর, এর তল পাওয়া কি চাড্ডিখানি কথা? হঠাৎ কী একটা কথা জ্যাবতীর মনের মধ্যে বুজকুড়ি কাটতে লাগল। কী যেন ভেবেছিল মহালয়ার দিন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে? সমুদ্দুর দেখবে, ছিখেত্তর যাবে, একা না, তার সব সই, সেনমশাই, খুড়িমা, ঠাকমা, পানু, এদিকে পিতাঠাকুর, মা পুণ্যির মা আর আদরের ভাই দুর্গাগতি। পিতাঠাকুর উঠোনে মাটির জালায় রাখা জল ঘাড়ে মুখে ছিটিয়ে গামছায় মুছছিলেন, এবার গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন, তারপর উঠে সন্ধ্যা আহ্নিক করে আবার পুথি লেখা, কোন কোনদিন একটি তরুণ আসে, বিপ্রদাস, তাঁর সঙ্গে তত্ব আলোচনা করতে। জয়াবতী আচমকা তাঁর কাছে গিয়ে বলল ‘পিতাঠাকুর, আপনি বলতে পারবেন একান থেকে ছিখেত্তর যেতে কত দিন লাগবে? আর কোন পথেই বা যেতে হয়?’
মেয়ের কথায় একেবারেই হকচকিয়ে গেলেন রামগতি। বোলসিদ্ধি থেকে সোনাটিকরি, এইটুকু গিয়েই মেয়ের পাখা গজাল নাকি? এ বংশের মেয়েদের দেখছি শিক্ষা একেবারেই সহ্য হয় না। সেই লক্ষ্মী সরস্বতীর কথাটা… তিনি গম্ভীর মুখে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দুয়ারে হারানের হাঁক শোনা গেল-
‘মাঠানরা, খরখর আসেন, দুখানা পালকিই এয়েচে’
পালকির বাহার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। ( ক্রমশ)
পুজোর গন্ধ
শ্রাবণী চক্রবর্তী
শহর ছেড়ে দূরে নাচছে তিনটে ফড়িং
সেই খুশিতে গান মনটি ওদের তাধিন
শরৎকাশের গুচ্ছ মাঝে ওরাই শুধু রঙিন।
ও মেয়ে তুই চললি কার খোঁজে
এক্কেবারে লাল পরীটি সেজে
পায়ে নুপুর মাথায় ময়ূরচুর
আকাশ দেখিস আল্হাদে ভরপুর
দ্যাখ বৃষ্টি এল খলখলিয়ে হেসে
একটু বাদেই রঙিন আকাশ
আহ্লাদেতে রোদেই যাবে ভেসে
রোদ বৃষ্টির বিচিত্র এই মাটি
দুর্গাপুজায় নাচছে ঢাকের কাঠি।
সঙ্গীত জগতে পাখির অবদান
শ্রীছন্দা বোস
প্রাণী জগতে এটি এক বিস্ময়কর যে পাখিরাই একমাত্র গান করতে পারে। সেও মাত্র কয়েকটি প্রজাতির পাখি, যাদের বলা হয় গায়ক পাখি। এদের মধ্যেও কেবল পুরুষদেরই গান গাইতে শোনা যায়।
কে জানে, হয়তো পাখিদের গান শুনেই আদিম মানুষের একদিন সাধ হয়েছিল গান গাইবার। আর তা থেকেই একটু একটু করে সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।
আমাদের খুব চেনা গায়ক পাখি হোল দোয়েল, কোকিল,বুলবুলি, শ্যামা, পাপিয়া এরা। আমাদের সঙ্গীতে মোট সাতটি স্বরকে নানাভাবে গেঁথেই সুরের সৃষ্টি করা হয়। সংক্ষেপে আমরা বলি, সা রে গা মা পা ধা নি। এর সঙ্গে যদি কোমল রে গা ধা নি আর কড়ি মা যোগ করি তাহলে দাঁড়ায় সবসুদ্ধ বারোটি স্বর। বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রতিটি স্বরের নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ আছে। স্কেল পরিবর্তন করলে সেই অনুযায়ী কম্পনাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরও পরিবর্তন হয়।উঁচুমানের শিল্পীরা এই বারোটি স্বরের মাঝখানে আরো স্বর আনতে পারেন যাদের বলা হয় শ্রুতি।
এবার আসি পাপিয়ার গানে। এদের গান বসন্ত কালেই শোনা যায়।
পুরুষ পাখিটি খুব উচু গাছের ডালে বসে গান ধরে ----"সা " থেকে শুরু করে কোমল কড়ি(কখনো শ্রুতিও) সমেত সবকয়টি স্বরই সে গেয়ে যায়। শেষে ' নি' তে পৌঁছে তিনবার বলে ওঠে পিউ কাঁহা। এর পর একটু বিরতি নিয়ে ফের শুরু করে ' সা' থেকে। কখনো কখনো সারারাত ধরে এরা গান গেয়ে চলে অবিশ্রাম, বিশেষ করে চাঁদনী রাতে। তাই বুঝি ইংরেজি তে এদের নাম Brain Fever Bird ! এই পাপিয়ার কাছ থেকেই আমরা সপ্ত সুরের সরগম পেয়েছি এমনটাই মনে হয় না কী?
গায়ক পাখি দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় নাইটিঙ্গেলকে। এই পাখিকে আমাদের দেশে বিশেষ দেখা যায় না, তবে ইউরোপে ও মধ্য প্রাচ্যে এরা সুপরিচিত।
শায়েরি ও গজল গানে যে ' বুলবুল ' এর কথা আছে সে আমাদের বুলবুলি নয় সে ঐ নাইটিঙ্গেল।
শোনাযায় কিছু বিখ্যাত সিমফনি রচিত হয়েছে ঐ পাখির গান কে অনুসরণ করে। ছোট্ট পাখিটি তার কণ্ঠস্বরে কী ভাবে এতটা বৈচিত্র আনতে পারে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।
আমাদের দেশে এর এক নিকট আত্মীয়কে দেখেছি --------- দার্জিলিং পাহাড়ের whistling thrush : আকারে প্রায় শালিকের মতো, গাঢ় বেগুনি ডানায় আবছা গোল গোল ছোপ, ঠোঁট হলুদ রঙের। পুরুষ ও স্ত্রী হুবহু একরকম দেখতে শুধু গান শুনে পার্থক্য বোঝা যায়।
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এরা খুব উঁচু এক জায়গায় গিয়ে বসে গান ধরে।
রোজই সে একই জায়গায় বসে তবে একই গান সে দুবার গায় না, প্রতিবারই নতুন কিছু সংযোজন বা কাটছাঁট করে। ভাবতে অবাক লাগে ঐ ছোট্ট মাথায় এতখানি সৃজনশীলতা কোত্থেকে আসে?
এই জাতীয় পাখিদের গান এতটা দ্রুত লয়ে যে আমাদের কানে ঠিকমতো ধরা পড়েনা, এ যেন ওস্তাদের গলায় গাওয়া তান। শিক্ষার্থীরা এই তান গুলিই প্রথমে ধীরে ধীরে ভেঙে ভেঙে গাইতে শেখে, পরে দ্রুত লয়ে অভ্যাস করে তেমনি এই পাখির গানকে যদি রেকর্ড করা যায় তারপর ধীর গতিতে শোনা যায় তখন তার মধ্যে পাওয়া যাবে এক অপূর্ব মেলোডি।
আমাদের সবার প্রিয় গায়ক পাখি অবশ্যই কোকিল।
কোকিলের ' কুহু' ডাক শুনেই রচিত হয়েছে কত গান, কত কাব্য। এদের গান বসন্ত ঋতু ছাড়িয়ে বৈশাখ মাস অবধি শোনা যায়। কোকিলরা স্কেল পরিবর্তনও করতে পারে ---- কু- উ- উ সে শুরু করে পঞ্চম স্বরে তারপর ক্রমে ক্রমে উঁচু থেকে উঁচুগ্রামে চড়তে থাকে, এক জায়গা অবধি উঠে কিছুক্ষন বিরতি নিয়ে ফের শুরু করে নিচু স্কেল থেকে।
চাঁদনী রাতে এরাও না ঘুমিয়ে সারারাত গান গেয়ে চলে মনের স্ফূর্তিতে। এই কোকিলই তো আমাদের দিয়েছে পঞ্চম স্বরটি যা মধ্যিখানে ধ্রুবক হয়ে থেকে সাতটি সুর কে এক সুতোয় গেঁথে রাখে, তাইতো ওদের কাছে আমরা ঋণী।
দোয়েল, ফিঙে, শ্যামা এদের গানেকি মেলোডি নেই? আছে বৈকি। তবে সেই গান বেশি সময় ধরে চলেনা। এটা লক্ষ করা যায়, অনেক সময় এরা একটা গানের কলি বারবার গেয়ে শোনাতে থাকে। পরে সেটাই আবার একটু অদল বদল করে গায়।
এইভাবে আপন খেয়ালে নিত্য নতুন গান বাঁধে এই খুদে গায়কেরা।
পাখিরা যে এতো যত্ন করে গান বাঁধে আর এতো মন দিয়ে গানের চর্চা করে সে কী শুধুমাত্র তার সঙ্গিনী পাখিকে শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করতে? নাকি নিজের প্রাণের আনন্দে? কিংবা এভাবেই ওরা দিনকে বরণ করে। হয়তো বা দিনমণি সূর্যকেই অভিনন্দন জানায়। যদি পাখিরা গান না গাইতো পৃথিবী কী এতো সুন্দর হতো?
নজরুলের সেই কবিতার লাইন গুলি মনে পড়ে-----
"ত্যজি নীড় করে ভীড়
ওড়ে পাখি আকাশে
এনতার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে,
বুলবুল চুলবুল শিস দেয়
পুষ্পে
এইবার এইবার খুকুমনি
উঠবে।"
রহস্যময় সেই ঘরটি
আকাশ মন্ডল
অষ্টম শ্রেণী, জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর
আজ শুক্রবার। দুপুরে লাঞ্চ করে হোস্টেলের গেটে ফেরার সময় বৃষ্টি শুরু হল। মনটা কীজানি কেন ভালো লাগছিল না। হঠাৎ ঘর যেতে ইচ্ছে করছিল। বিকেলে স্যাঙ্কস খেয়ে সেলফ স্টাডিতে গিয়ে বন্ধুদের বললাম, কাল লিভ নিয়ে বাড়ি যাব দুদিনের জন্য, তোরা আমায় ব্যাগ গোছাতে সাহায্য করবি তো? কেউ সাড়া শব্দ করল না। আমিও রেগে মেগে লাইব্রেরি থেকে নেওয়া ভূতের বইটা বার করে পড়তে শুরু করলাম। ভূতের গল্প পড়তে আমার দারুণ লাগে। রাত আটটায় ডিনার করে হোস্টেলে ফিরে দেখি আমার বন্ধুরা আমার ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছে। আমি একই সঙ্গে খুশি ও লজ্জিত হলাম। খুশি হলাম কারণ, আমার বন্ধুরা আমার সব কাজ করে দিয়েছে। আর লজ্জিত হলাম কারণ, আমি আমার বন্ধুদেরকে ভুল বুঝেছিলাম। তারপর ওদের সঙ্গে একটু গল্প করে শুতে চলে গেলাম। আর যতক্ষণ ঘুম এল না, ততক্ষণ ভূতের গল্পগুলো পড়লাম। সকাল সকাল রওনা দেব ভেবেও ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। তাই সাতটা নাগাদ উঠে গেট পাস নিয়ে বেরোতে বেরোতে বেশ দেরি হয়ে গেল। তখনও আমি জানতাম না এই যাত্রাটা আমার কাছে কতটা রোমাঞ্চকর হবে।
আমাদের স্কুল থেকে রেলস্টেশন একটু দূরে ছিল আর সেখানে যাওয়ার কোনো বাসও ছিল না। হেঁটে হেঁটে একটু এগোতেই হঠাৎ বৃষ্টি নামল। য়ার আমার সঙ্গে ছাতাও ছিল না। এমনকি কাছাকাছি দাঁড়ানোর কোন জায়গাও ছিল না। তাই ভিজে ভিজেই কিছুটা এদোতে একটা রিক্সা পেলাম। কিছুটা এগোতেই অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। একজন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকু এখানে এত গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?
কাকু বলল, এখন ব্রিজের ওপর নিচে অনেক জল দাঁড়িয়ে গেছে বলে গাড়ি চলছে না।
আমি বললাম, কতক্ষণে জল নামবে?
কাকু বলল, বৃষ্টি না থামলে কিছু বলা যাবে না।
আমি বললাম, আর কোনো রাস্তা নেই উদয়পুর স্টেশনে যাবার?
কাকু বলল, হ্যাঁ, একটা রাস্তা আছে তবে সেটা অনেক ঘুর পথ হবে।
আমি বললাম, ঠিক আছে। তবু সেই রাস্তা দিয়েই চলো, রিক্সা কাকু।
তখন মনে মনে ভাবলাম, আগে যদি জানতামতাহলে আজ না বেরিয়ে কাল আসতাম। যাক, অনেক ঘুরে হলেও শেষে স্টেশনে পৌঁছোলাম। কিন্তু গিয়ে শুনি ট্রেন অনেক আগেই চলে গেছে। স্টেশনের বেঞ্চে বসে ভূতের বইটা পড়তে লাগলাম। সন্ধে ছ’টা হবে তখন পরের ট্রেনটা এল। আমি কিছু খেয়ে সেটায় উঠে পড়লাম।
শিবরামপুর স্টেশন পৌঁছাতে রাত ন’টা হল। বৃষ্টি তখন একটু কমেছে। আমি ট্রেন থেকে থেমেই ঘরের রাস্তা ধরলাম। কিছুটা যাবার পর আবার বৃষ্টি শুরু হল। তখন দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজতে খুঁজতে একটা ঘর দেখতে পেলাম, ছুটে সেদিকে গেলাম। ঘরের সামনে একটা নেমপ্লেটে ইংরাজিতে লেখা মি ইন্দ্রজিৎ, তারপর ভাঙ্গা। আর পড়া যাচ্ছে না। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলাম, ঝুল আর মাকড়সায় ভর্তি। আমি ঘরে ঢুকে যেতেই দরজাটা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এক কোণে বসে চোখ বুজে রইলাম। পুরো রাত বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কারো যাবার, কিছু ভাঙ্গার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন মনে হল এসবই ব্যাগে রাখা ভূতের বইটার জন্য হচ্ছে না তো? মনে হতেই বইটা ব্যাগ থেকে বার করে পাশে রাখলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেই জানি না।
সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি আমি অনেক বড়ো একটা মাঠে একা শুয়ে আছি। তখন বৃষ্টি না হলেও কালো মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল। আমি ছুট লাগালাম। খানিকটা ছুটে মাঠ পেরোতেই আমি ঘর যাবার চেনা পথ খুঁজে পেলাম। ঘর পৌঁছোতেই মা জিজ্ঞেস করল, তুই এত হাঁপাচ্ছিস কেন?
আমি বললাম, ছুটে ছুটে এসেছি তাই।
মা বলল, তোর তো কাল আসার কথা ছিল।
আমি আমতা আমতা করে বললাম, ঐ ট্রেন লেট ছিল বৃষ্টির জন্য। তাই রাতে স্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে স্কুলে ফিরলাম। ফিরেই বন্ধুদের সেই রোমাঞ্চকর রাতের কথা বললাম। কেউ বলল, ঐ ঘরটা ভুতুড়ে, কেউ বলল, ওটা তোর মনের ভ্রম। রুটিনে এরপর লাইব্রেরি ক্লাস দেখে মনে পড়ে গেল, লাইব্রেরির বইটাতো আমি ঐ ভুতুড়ে ঘরে রেখে এসেছি। কিন্তু বইটাতো লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতেই হবে। তার মানে আমাকে আবার সেই ভুতুড়ে ঘরে যেতে হবে!
স্মরণীয়
( শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
পীযূষ প্রতিহার
১৮৭৬ সালের ১৫সেপটেম্বর অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার অবিসংবাদিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ার নিকট মামুদপুরে। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল দেবানন্দপুরের প্যারী পন্ডিতের পাঠশালায়। এরপর ভাগলপুরে মাতুলালয়ে থাকাকালীন মামা মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ভর্তি করে দেন দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে। ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৯ সালে দেবানন্দপুর ফিরে এসে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। তীব্র দারিদ্রতার কারণে ফি দিতে না পারায় তাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। এই সময় 'কাশীনাথ' ও 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে দুটি গল্প লেখেন তিনি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মামার সঙ্গে পুনরায় ভাগলপুর ফিরে গেলে সেখানে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় তেজনারায়ন জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হন কিন্তু পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারায় এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। এভাবেই শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর।
এরপর ভাগলপুরে কিছুদিন থাকাকালীন একটি সাহিত্য আড্ডা শুরু করেন। এই সাহিত্যের আড্ডার সময়কালে রচনা করেন 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শুভদা' ইত্যাদি উপন্যাস ও 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'হরিচরণ' ইত্যাদি গল্প। এই সময় তিনি বনেলী রাজ এস্টেটে কিছুদিন চাকরিও করেন। এই সময় পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে গৃহত্যাগী হন। পরে পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে ভাগলপুরে ফিরে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন ও কলকাতা চলে আসেন। কলকাতায় উকিল লালমোহন গাঙ্গুলির বাড়ীতে হিন্দি বই থেকে ইংরেজি অনুবাদ করার কাজ করতে শুরু করেন। তখনই 'মন্দির' নামে একটি ছোটগল্প লেখেন ও 'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। এটিই ছিল তাঁর লেখা প্রথম মুদ্রিত গল্প। মাত্র ছয় মাস কলকাতায় থেকে ১৯০৩ সালের শুরুতে রেঙ্গুনে চলে যান ও বর্মা রেলওয়ে অডিট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরি নেন। দুবছর পর চাকরি চলে গেলে তাঁর বন্ধু গিরিন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগু চলে যান। ১৯০৬ এর এপ্রিল মাসে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসের ডেপুটি এক্সামিনার মনীন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনের এই অফিসে চাকরি পান। প্রায় দশবছর এখানে চাকরি করেছিলেন তিনি।
১৯১২ সালে কিছুদিনের ছুটিতে কলকাতায় এলে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের থেকে প্রকাশের জন্য লেখা চাইলে তিনি বর্মায় গিয়ে 'রামের সুমতি' গল্পটি পাঠান। যেটি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্যও লেখা পাঠিয়েছিলেন তিনি। ফণীন্দ্রনাথই তাঁর লেখা 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রথম প্রকাশ করেন। 'যমুনা' পত্রিকায় অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য', 'কানকাটা', 'গুরু শিষ্য সংবাদ' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। কিছুদিন স্বদেশী আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসটি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৫ সালে সেটি বাজেয়াপ্ত করে। তিনি মোট কুড়িটি উপন্যাস, চারটি নাটক, বারোটি প্রবন্ধ ও একুশটি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের লেখাগুলোর মধ্যে 'বিন্দুর ছেলে', 'শ্রীকান্ত' (৪খন্ড), 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা', পন্ডিতমশায়, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, শেষ প্রশ্ন, 'বড়দিদি' ইত্যাদি উপন্যাস; 'বিরাজ বৌ', 'ষোড়শী', 'বিজয়া' ইত্যাদি নাটক; 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি গল্প এবং 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিখ্যাত। তাঁর বহু রচনা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় একাধিকবার চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।
সাহিত্য সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্র নানা সম্মান পেয়েছেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিনী পদক পান সাহিত্যে অবদানের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩৬ সালে সাম্মানিক ডি লিট দিয়ে সম্মানিত করে।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ জীবনের বেশ কিছুদিন কেটেছিল হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে। রূপনারায়ণের তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। শরৎচন্দ্র ১৯৩৭ সালে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিন-চারমাস হাওয়া বদলের জন্য থেকেছিলেন দেওঘরে। দেওঘর থেকে ফিরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। যকৃতের ক্যান্সার ধরা পড়ে তাঁর। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় জীবনাবসান হয় এই অবিস্মরণীয় কথাশিল্পীর।
পাঠ প্রতিক্রিয়া
(ছোটোবেলা ৯৮ পড়ে দোলনচাঁপা তেওয়ারী যা লিখলেন)
"জ্বলদর্চি ছোটবেলা" ৯৮ লিখতে গিয়ে প্রতিবারের মতো এবারেও সম্পাদকীয়তেই মৌসুমী দি খুব সুন্দর করে পত্রিকারটির সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন।
ধারাবাহিক উপন্যাস তৃষ্ণা বসাকের লেখা "জয়াবতীর জয়যাত্রা"য় লেখক চারটি সুন্দর মেয়ের কথা বলেছেন এবং তাদের মা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যিই তো আমরা মেয়েরা তো "মা" এরই অংশ। কত বড় ভাবনা।
এরপরই চোখ চলে গেল দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী প্রীতিলতা ঠাকুরের আঁকা একটা সুন্দর প্রজাপতির ছবির উপরে।
লেখক তারা প্রসাদ সাঁতরা
"সুরদাস" কবিতাটি তে শিয়ালকে নিয়ে বেশ হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, পড়ে বেশ মজা পেলাম।
আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর ছোট্ট বন্ধু শুভঙ্কর সেন কি সুন্দর একটা রোবট এঁকেছে।
এরপরে পারমিতা মন্ডলের লেখা একটা সুন্দর শিক্ষনীয় গল্প 'ভূল" পড়ে ফেললাম। সত্যিই তো বাচ্চাদের শুধু উৎসাহ দিতে হয় তাহলেই তারা সামনে দিকে এগিয়ে যাবেই যাবে।
ইউকেজির মিষ্টি মেয়ে প্রীতিশা পাল তারই মত একটা মিষ্টি জাহাজ এঁকে ফেলেছে।
নবম শ্রেণীর ছাত্র অঙ্কিত ঘোষের "কিছু সময়" গল্পটা পড়ে বেশ বুঝছি একালের বাচ্চারাও একান্নবর্তী পরিবারেই থাকতে চায়, বাবা-মা,দাদু দীদা দের সঙ্গে। গল্পটিতে একটি পজিটিভ ভাবনা কাজ করেছে। বাবাই এর মত দাদুর জন্য আমারও মন খারাপ হয়ে গেল।
এবারের স্মরণীয় বিভাগে লেখক পীযূষ প্রতিহার নাট্যকার ও নাট্য অভিনেতা শম্ভু মিত্র কে নিয়ে লেখেছেন তিনি ভারতীয় থিয়েটারকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। এই লেখা থেকে শম্ভু মিত্র সম্পর্কে আরো অনেক নতুন তথ্য পেলাম ধন্যবাদ জানাই লেখক কে।
আবারও শেষে সম্পাদক মহাশয়া মৌসুমীদি কে ধন্যবাদ জানাই "জ্বলদর্চি ছোটবেলা" কে এক ম্যাজিক নাম্বারের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
আরও পড়ুন



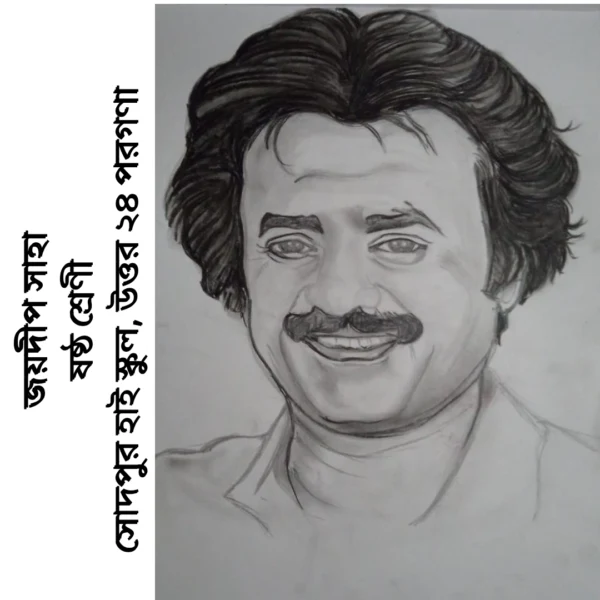
















0 Comments