অক্ষয়-সাগর
প্রসূন কাঞ্জিলাল
১৫ জুলাই, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় নবদ্বীপের কাছে চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন উনিশ শতকের নবজাগরণের বাহকদের মধ্যে অন্যতম অক্ষয় কুমার দত্ত। ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং লেখক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা এবং স্কুলপাঠ্য বইয়ে অতি সহজ-সরল ভাষায় বিজ্ঞানের ধারণা দানের প্রয়াসে তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক। অক্ষয়কুমার সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে লেখক জীবন শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তিনি মূলত ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলি বাংলায় অনুবাদ করতেন। ১৮৩৯ সালে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য মনোনীত হন এবং কিছুদিন সভার সহ-সম্পাদকও ছিলেন। ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৪২ সালে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যাদর্শন নামের একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেন। লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভের কারণে ১৮৪৩ সালে তাকে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে মনোনীত করা হয়। তিনি ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের নির্ভীক মতামত (জমিদারি প্রথা, নীলচাষ, ইত্যাদি সম্পর্কিত মতামত) প্রকাশ পেত। এই সব প্রবন্ধ তিনি পরে বই আকারে বার করতেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে অক্ষয়কুমার বুদ্ধিজীবী বাঙালী মানসের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার, ভূগোল (১৮৪১), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫২; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩), চারুপাঠ (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ- ১৮৫৪, ৩য় খণ্ড- ১৮৫৯), ধর্মনীতি (১৮৫৫), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ- ১৮৭০, ২য় ভাগ- ১৮৮৩)।
🍂

ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব সংগঠন "তত্ত্ববোধিনী সভা" গঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার এবং ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালে জন্ম হয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"। পত্রিকার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকার জন্য রীতিমতো পরীক্ষা নিয়ে সম্পাদক হিসেবে "অক্ষয় কুমার দত্ত" মহাশয়কে নিযুক্ত করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর , ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর , রাজনারায়ণ বসু ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে জীবনের প্রায় শেষ লগ্ন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ছিলেন এই পত্রিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত
কিছু মনোজ্ঞ তথ্য এবং শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদ্যতার সূচনা ও গভীরতা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা থেকে জানা যায় -----
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাই লিখতেন, আনন্দকৃষ্ণ বাবু প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের তা দেখে আবশ্যকমত, সংশোধনাদি করে দিতে হত। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসেছিলেন, এমন সময় অক্ষয়কুমার বাবুর একটা লেখা সেখানে উপস্থিত হয়। আনন্দ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাটা পড়ে শুনিয়ে দেন। অক্ষয়কুমার বাবু পূর্ব্বে যে সব অনুবাদ করতেন, তাতে কিছুটা ইংরেজি ভাব থাকত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর লেখা দেখে বলে ছিলেন ,—“লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে।” আনন্দকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তা সংশোধন করে দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করে দেন। এইরূপ তিনি বার কতক সংশোধন করে দিয়েছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখে বড়ই আনন্দিত হতেন। তখনও কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানতেন না। লোক দ্বারা প্রবন্ধ পাঠানো হত এবং লোক দ্বারাই ফিরে আসত। তিনি সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখে ভাবতেন,— এমন বাঙ্গালা কে লেখে ? কৌতুহল নিবারণের জন্য তিনি এক দিন স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় পান। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। এর পর অক্ষয় বাবু যাহা কিছু লিখতেন, তা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়ে নিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করে দিতেন। পরস্পরের প্রগাঢ় সৌহার্দ্য সংগঠিত হয়।
অক্ষয়কুমার বাবুর প্রস্তাবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণের সমর্থনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত “পেপার-কমিটীর” অন্যতম সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সূত্রে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথেও সংযুক্ত হয়েছিলেন। তবে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। “পেপার কমিটী” বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংস্রবে, ধর্ম্মের টানে নয় ।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করবার পূর্বে , অক্ষয় বাবুকে ও সেই সম্বন্ধে “পেপার-কমিটী”র সভ্যদিগের মতামত নিতে হত। তার একটা প্রমাণ দেওয়া হলো ---
“কবিপন্থীদিগের বৃত্তান্ত-বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি, যথাবিহিত অনুমতি করিবেন।”
তত্ত্ববোধিনী সভা,
শ্ৰী অক্ষয়কুমার দত্ত,
১৭৭০ শক, ১৪ই আষাঢ় ।
“গ্রন্থ-সম্পাদক"।
“প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম।
ইতি —
“শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্ৰ শর্মা ”
“শ্ৰীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।”
-'তারাচরণ মুখোপাধ্যায়'।
যদিও পত্রিকার পথ চলা শুরু হয় মূলত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও বেদান্ত সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অচিরেই এই পত্রিকায় ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ হতে থাকে।
সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের ইচ্ছা এবং বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। একটা পর্যায়ে এসে সম্পাদক অক্ষয়কুমারের সাথে নিয়োগকর্তা দেবেন্দ্রনাথের নিয়মিত তর্ক-বিতর্ক ও মতান্তর ঘটেছে মূলতঃ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর বিভিন্ন লেখাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল অক্ষয়কুমারের পক্ষে। এই সময় বিদ্যাসাগর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তত্ত্ববোধিনীর পথ নির্নয় এবং গুনমান নির্ধারণে। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ এমনকি কখনো কখনো সম্পাদকীয় ও লিখতে হতো বিদ্যাসাগরকে। ক্রমশ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বের আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনই তত্ত্ববোধিনীকে ওই উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে বিদ্যাসাগরের অবদানকেও স্বীকার না করার স্পর্ধাও করা যায় না।
সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাব বিজড়িত দেখে এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঠিক মতমিল হচ্ছে না বুঝে , অক্ষয়কুমার দত্তের কিছু কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দুই জন স্বাধীন-চেতা ও তেজস্বী পুরুষের মতসংঘর্ষে পরিণাম এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়।চক্মকী পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষণে অগ্নিফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়ই ।
বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য উদাহরণযোগ্য।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমমননের এক সম্পাদককের পৃষ্ঠপোষকতাও অনিবার্য।
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা’। কথাটি অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পর্কেও সমানভাবে সত্য। তিনি বিদ্যসাগরের পরম বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা দুজনই যুগপৎভাবে বাংলা ভাষা গদ্যের মজবুত ও আধুনিক ভিত্তি নির্মাণ করে গেছেন। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা বিকশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ, একজন উৎকৃষ্ট চিন্তাবিদ এবং প্রথম বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী।
অক্ষয়কুমার দত্ত ‘বিদ্যাদর্শন’ নামক একটি মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন কিছুদিন।1855 সালের 17 জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল। উদ্দেশ্য - বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত আদর্শ স্কুল ( Normal School ) স্হাপন করেছেন বিদ্যাসাগর, সেই সমস্ত স্কুলের জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। নর্মাল স্কুলটি দুটি ভাগে বিভক্ত। উচ্চ শ্রেণির ভার নিলেন প্রধানশিক্ষক শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্তকে শ্রদ্ধা করতেন বিদ্যাসাগর। দুজনেই সমবয়সী। কয়েক মাসের বড় অক্ষয় দত্ত। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে তাই বিদ্যাসাগর চিঠিতে লিখলেন -
" For the post of Head Master of the Normal classes, I would recommend Babu Akshay Kumar Dutt, the well known editor of the 'Tatwabodhini Patrika'. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge, and well acquainted with the art of teaching."
দীর্ঘদিন অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শারীরিক কারণে যখন পত্রিকার কাজ থেকে বিরতি চাইছিলেন তখনি বিদ্যাসাগর তাঁকে নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদটি প্রদান করেন। শুধুই কি শারীরিক কারণ ? সে সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যও সর্বজনবিদিত। কারণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে লিখছেন --
" কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে এই পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"
এর পর পরই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী ছেড়ে দেন। কেউ বলে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তর অন্যতম জীবনীকার, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস তাঁর "অক্ষয় চরিত" (1887) বইতে লিখেছেন নর্মাল স্কুলের কাজ পেয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন -- "তাহলে বাঁচি।" যদিও দ্বিমত রয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রী আশীষ লাহিড়ী মহাশয় তাঁর "আঁধার রাতে একলা পথিক" বইতে অক্ষয়কুমারের এই মতামতকে খণ্ডন করে অক্ষয়কুমারের আরেক জীবনীকার মহেন্দ্র রায়ের বিবরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার জীবিত থাকা কালেই প্রকাশিত হয় মহেন্দ্র রায়ের "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত"(1887)। সেখানে মহেন্দ্র রায় লিখেছেন তাঁর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে বলে মাসিক তিনশ টাকা মাইনের এই পদ নিতে অস্বীকার করেছিলেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু বিদ্যাসাগর যেহেতু আগেই চিঠি লিখে শিক্ষাধ্যক্ষের অনুমতি আদায় করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মর্যাদার কথা ভেবে কিছুটা নিমরাজি হয়েই অক্ষয়কুমার এই পদে যোগদান করেন। তবে বেশিদিন এই কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেননি তাঁর শিরঃপীড়ার জন্য। বারবার অজ্ঞান হয়ে যেতেন। 1858 সালে তাই ছেড়েও দেন শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুলের অধ্যক্ষের পদ। নিজের পড়াশোনা, লেখালিখির প্রতি মনোযোগী হন তিনি।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান শিক্ষার পথিকৃৎ শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের উপর লেখা কিছূ সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্য চয়ন : ----
1. অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক- আশীষ লাহিড়ী(2019), দ্বিতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং
2. সেকালের কৃতী বাঙালি-- মন্মথনাথ ঘোষ(2020)
3. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (প্রথম খণ্ড) ---- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ(2016)
4. History of the Brahmo Samaj-- Shivnath Sastri(1993)
5. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী
6. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক-- সম্পাদনা: প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত(1426)
7. উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্র- স্বপন বসু(2018)
8. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কামারের এক ঘা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইন্সটিটিউট
9. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান.
10. অক্ষয় কুমার দত্ত, বিস্মৃত অবিস্মৃত - পীযূষ কান্তি সরকার।
11. গদ্য শিল্পী অক্ষয় কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর --- নবেন্দু সেন।


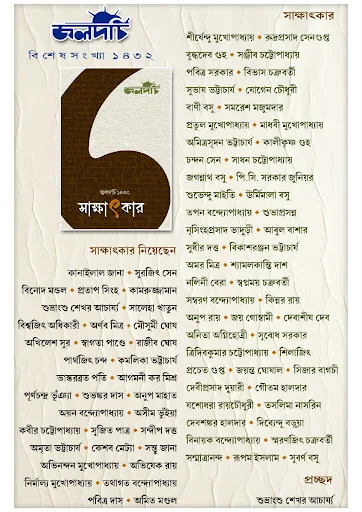












0 Comments