শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানেরা
প্রীতম সেনগুপ্ত
নিবেদিতা ভারতে আসেন ১৮৯৮ সালে। ভারতে পদার্পণকালে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বিষয়ে তিনি লিখছেন – “গঙ্গাতীরস্থ শষ্পাবৃত ভূমি ও বৃক্ষরাজির মধ্যেই, যে লোকগুরুর কার্যে ইতিপূর্বেই আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সম্বন্ধে জানতে পারি। আমার ভারতে পদার্পণকালে ( ১৮৯৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারি ) বেলুড়ে সবেমাত্র একখণ্ড জমি ও একটি বাড়ি ক্রয় করা হইয়াছিল; তাহাই পরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মঠরূপে পরিণত হয়। আরও কয়েক সপ্তাহ পরে আমেরিকা হইতে কয়েকজন বন্ধু আগমন করেন এবং স্বভাবগত সাহসিকতার সহিত ঐ অর্ধজীর্ণ বাড়িটি অধিকার করিয়া উহাকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দভাবে বাসের উপযোগী করিয়া লন। এই বন্ধুগণের অতিথিরূপে বেলুড়ে বাসকালে, এবং পরে কুমায়ুন ও কাশ্মীর ভ্রমণকালেই আমি তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষকে ভাল করিয়া চিনিতে ও স্বদেশে স্বজনগণের মধ্যে স্বামীজীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হই ।
আমাদের বাড়িটি ছিল কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে নিম্ন সমতলভূমির উপরে নির্মিত। জোয়ারের সময় পানসির ন্যায় ছোট ছোট নৌকাগুলি ( গঙ্গাতীরে যাহারা বাস করে, এই নৌকাগুলি তাহাদের যানবাহনের কাজ করে ) একেবারে সিঁড়ির নিচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের ও অপর পারের গ্রামের মধ্যে নদীটির বিস্তার ছিল অর্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল। নদীর পূর্বতীরে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত। মন্দিরসংলগ্ন এই উদ্যানেই স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বাস করিতেন। যে বাড়িটি এখন মঠরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের কুটির হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত ছিল। মঠবাড়ি ও আমাদের কুটিরের মধ্যে অনেকগুলি বাগানবাড়ি এবং অন্ততঃ একটি নালা ছিল। তালগাছের গুঁড়ি চিরিয়া তাহার অর্ধাংশ দ্বারা নির্মিত একটি পুলের উপর দিয়া নালাটি পার হইতে হইত; পুলটি দেখিলে সন্দেহ হইত, ভার সহিতে পারিবে কি না।
🍂

আমাদের এই বাড়িতেই স্বামীজী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী অথবা কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ আসিতেন। এখানেই প্রাতঃকালীন জলযোগ সমাপ্ত হইবার পর বৃক্ষতলে বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা স্বামীজীর অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভারতীয় জগতের কোন না কোন গভীর রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করিতেন।” ( স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক – স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় )
১৮৯৭ সালের ১১ মে বিবেকানন্দসহ একটি বড়সড় দল আলমোড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ছাড়া সেই দলে ছিলেন নিরঞ্জননানন্দ, সদানন্দ, স্বরূপানন্দ, যোগীন-মা, জয়া ( জো ), ধীরামাতা ( মিসেস বুল ) ও নিবেদিতা। এছাড়াও ছিলেন কলকাতাস্থ মার্কিন-কনসাল - জেনারেলের স্ত্রী মিসেস প্যাটারসন। আমেরিকায় স্বামীজী এই প্যাটারসনদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে এই ভ্রমণকারী দলটি কাঠগোদামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সমগ্র পথটি ছিল দু’রাত একদিনের। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল হয়ে আলমোড়া যাওয়াই ছিল গন্তব্য পথ। এই প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা মাতাজী লিখছেন –“সেই ব্রিটিশশাসিত ভারতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চারজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার ভ্রমণ অবশ্যই অনেকের ( বিশেষত সাহেবসুবোদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তার ফলে চাপা গলায় ফিসফাস, উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্য সমালোচনা এবং টিটকিরি, অপমান সবই সহ্য করতে হয়েছিল তাঁদের। একদিক থেকে দৃশ্যটা তো অদ্ভুত। সুসজ্জিতা, অভিজাত মহিলারা চলেছেন – তাঁদের পিছন পিছন গুচ্ছের ট্রাঙ্ক, সুটকেসের বোঝা মাথায় নিয়ে কুলিরা; আর তাঁদেরই সঙ্গে চলেছেন গেরুয়া পরা কয়েকজন সাধু। হাতে তাঁদের একটা করে পুঁটুলি, এবং সম্ভবত একটা করে কালো ছাতা ও কমণ্ডলু! কলকাতার সমাজে মান-মর্যাদার বিচারে মিসেস প্যাটারসনই সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এই সাহসিকতার পরিচয় কয়েকবছর আগে তিনি আমেরিকাতেও দিয়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গ না হওয়ার দরুণ কোনো হোটেলেই যখন স্বামীজী প্রবেশাধিকার পাচ্ছিলেন না তখন তিনিই বিবেকানন্দকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন আর তার জন্য তাঁকে অনেক সমালোচনা সইতে হয়েছিল। এতো গেল বিদেশী সাহেবসুবোদের প্রতিক্রিয়া। অন্যদিকে আবার নিজের দেশের লোকেরাই ‘মেমসাহেবদের’ সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর জন্য সাধুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগলেন।…
ট্রেনে যেতে যেতে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বহু তথ্য আহরণ করে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বৈপরীত্য সরস আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরে বিবেকানন্দ তাঁর ভ্রমণসঙ্গীদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল নগর ও জনপদগুলির পাশ দিয়ে তাঁদের ট্রেন ছুটে চলেছে; দৃশ্যপটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে বিবেকানন্দের বর্ণনা। ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান শিবপুরী কাশী, যেখানে মন্দিরপ্রাঙ্গনে বসে ব্রাহ্মণ শিশুরা বেদ আবৃত্তি করে, তার উপকণ্ঠ দিয়ে বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত পাটনা ও লক্ষ্ণৌ শহর – এসবকিছু পিছনে ফেলে রেখে ট্রেন দ্রুত ধেয়ে চলেছে। অজস্র বর্ণাঢ্য ছবি তাঁদের চোখের সামনে এসেই আবার নিমেষে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে যখনই হাতি বা উটের পাল দেখা গেছে, তখনই বিবেকানন্দ তাঁর অনুপম কথার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন অতীতের যুদ্ধবিগ্রহের ধুন্ধুমার কোনো দৃশ্য, নয়তো রাজা-রাজড়া এবং মোঘল দরবারের আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ উজ্জ্বল কোনো ছবি। গোধূলি বেলায় যখন গরুর পালের ঘরে ফেরার দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ত অথবা সরল, ধর্মনিষ্ঠ দরিদ্র গ্রামবাসীর শান্ত জীবনের টুকরো কোনো ছবি সহসা তাঁদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে, অথবা প্রার্থনারত মুসলমান এবং পূজায় নিরত হিন্দুদের ভক্তির নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তখনই ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকটি তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতেন। আর বিবেকানন্দের সঙ্গীরাও যেন বহু যুগ পেরিয়ে এসে অতীতের রঙ-রূপ-রেখায় চিত্রিত ছবিগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।” ( জোসেফিন ম্যাকলাউড, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর )
স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য অনুগামিনীদের চিনিয়েছিলেন ভারতের হৃদস্পন্দন। তিনি জানতেন ভারতের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এঁরা ( নিবেদিতা বিশেষত ) প্রাণপাত করবে। আর এই সেবাকাজটি চালাতে গেলে এঁদের প্রাথমিকভাবে চিনিয়ে দিতে হবে এই অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশটিকে। তাঁর সমস্ত জ্ঞানরাশি যেন উন্মুক্তদ্বার হয়ে উঠেছিল এঁদের জন্য। এক অতি অদ্ভুত অনুপ্রেরণা, আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন এঁদের মধ্যে। এর ফল যা হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে বিরাজমান। হিমালয়ে বিশেষ করে কাশ্মীরে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা, ম্যাকলাউড প্রমুখের এক দৈব সময় যাপিত হয়েছিল। মহামায়ার অসীম কৃপায় তাঁরা চিনেছিলেন এই দেশের আত্মাকে, শুধু চেনেন নি, হয়ে উঠেছিলেন ভারতের। ভারতাত্মার গৌরবময় ধ্বজা বহন করেছিলেন।

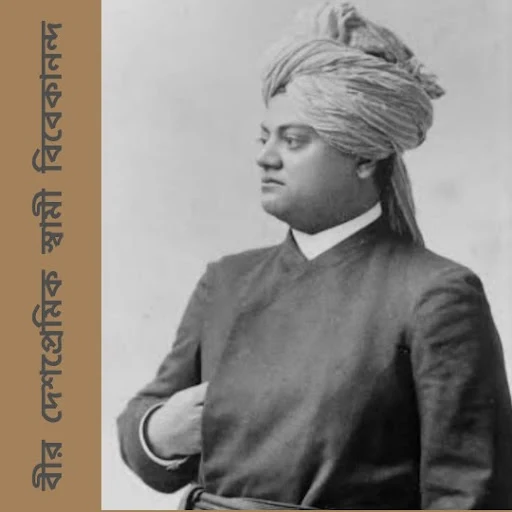














0 Comments