যে সব কথা লেখা হয় না-৩সুমনা সাহা
ছোটবেলার কথা মনে হলেই একসঙ্গে এত স্মৃতি হুড়মুড় করে এসে ভীড় করে যে কোনটা রেখে কোনটা বলব, থৈ পাই না। গল্পের বইগুলো যেন জীবন্ত মানুষের মত সঙ্গী ছিল। চরিত্রগুলো জ্যান্ত হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াত আমাদের সঙ্গেই। গল্পের চরিত্রদের নামে বাড়িতে আসা কোন অতিথি বা আগন্তুকের নাম রাখা হচ্ছে, কখনো বা পুকুরে, কখনো বাগানে, কখনো বিশেষ কোনও গাছতলায় পাতার স্তুপের নিচে আবিষ্কার করছি নানা গুপ্ত কুঠুরি, যাদুকরীর আস্তানা বা পাতালের রাস্তা। ঘুঘু ডাকা নির্জন দুপুরে যখন গাছের নিচে পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ্দুর ছায়ার সঙ্গে কাটাকুটি খেলত, আমি সহজ পাঠের সেই পাড়াটাকে দেখতে পেতাম—‘ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি, আছে আমাদের পাড়াখানি/দীঘি তার মাঝখানটিতে, তালবন তারি চারিভিতে।’ দুপুরবেলাকার নিঝুম পাড়ার ঐ ঘুঘুর ডাক, কুবো পাখির একটানা কুব কুব শব্দ, আলোছায়ার মায়া, পুকুরের জলে মাঝে মাঝে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ছে মাছরাঙা, উড়ে যাওয়ার সময় রোদে মেলে দিচ্ছে তার নীলাম্বরীর মতো সুন্দর ডানা—কি অপূর্ব একটা সৌন্দর্যানুভূতির ভাব উঠত মনে, ছোট্ট আমি সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারতাম না, কিন্তু মনটা যেন সবটুকু আলো হাওয়া মেখে নিয়ে ছুট লাগাতে চাইত। মা কিছুতেই দুপুরে বাইরে বেরোনোর পারমিশন দিত না। সকালবেলার স্কুল। তাই ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠতে হত। দুপুর বেলা একটুকুনি ঘুমাতেই হবে। ঘুম কি আর আসে? বিছানায় শুয়ে শুধু উশখুশ। বেশি নড়াচড়া করলেই মা মুখে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করত আর বলত, “আহ! বাচ্চাগুলোর জ্বালায় একফোঁটা শান্তি নেই!” কখন মা বলবে, “ঠিক আছে, এইবার যা খেলতে”, এইটা শোনার জন্য চোখ খিটিমিটি করে টিপে শুয়ে থাকতাম। যেই না মায়ের আদেশ হল, অমনি ‘হুররে’ বলে দুই বোন লাফিয়ে বিছানার বাইরে। বিছানাটা ছিল গড়ের মাঠের মত বিশাল। দুপাশে কাঠের রেলিং দেওয়া, যাতে বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে ছটফট করলে পড়ে না যায়, অর্ডার দিয়ে তৈরি করা। একসঙ্গে ৬-৭ জন অনায়াসে শুতে পারবে। অবশ্য ছোটবেলার স্মৃতিতে সবই বিশাল মনে হয়। পরে সেসব দেখে করুণা হয়েছে, এমনও স্মৃতি আছে। সেকথাও বলব। তবে বৃষ্টির দিনগুলো বাড়িতেই কাটত। তখন রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান শুনতাম, নাটক শুনতাম। বোরোলিনের সংসার, শনিবারের বারবেলা এগুলো ছিল বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান।
🍂

বিবিধভারতীর হিন্দি গান বাবার সামনে শোনা যেত না। বাবার মেজাজ খুব গরম ছিল। আমাদের কড়া শাসনে রাখতেন। কলেজে পড়ার আগে পর্যন্ত ঠোঁটে ‘লিপিস্টিক’ লাগাতে পারিনি। বাবার সামনে মাথা আঁচড়ালেও রেগে যেতেন, বড়দের সামনে কেশচর্চা প্রায় অশ্লীলতার সমান গণ্য করা হত। ওদিকে দাদা তো কলেজে যাওয়ার আগে রোজ স্নান করে ভেজা চুলে টেরি কাটত দাড়ি কামানোর ছোট আয়নার সামনে। তখন সব যুবকেরই রাজেশ খান্নার মত চুলে শিঙাড়া কাট, দুদিকে চাপা, মাঝখানে হাত দিয়ে চেপে চূড়ার মত একটু উঁচু করা, লম্বা জুলপি। দাদা ভাল শিস দিতে পারত। প্রায় সব হিন্দি গানই শিস দিয়ে গাইত। বাবার অনুপস্থিতিতে আমাদের ফরমায়েসে একের পর এক ‘জিন্দেগি এক সফর হ্যায় সুহানা’, ‘মেরি সপ্নো কি রানী কব আয়েগি তু, ‘কুছ তো লোগ কহেঙ্গে’ এইসব গানে শিস দিয়ে সুর তুলত। আমরা ছিলাম ওর তীক্ষ্ণ সমালোচক। “না না এখানে সুর ঠিকঠাক হল না, ওইখানটা তাল কেটে গেল” শুনে শুনে দাদা শিস রিফাইন করত। জেঠুর পাঁচ ছেলের মধ্যে বড়জন আমার বাবার খুব আদরের ভাইপো। দাদাকে বাবা খুব ভালবাসত। দাদাও কাকু বলতে অজ্ঞান। জেঠু যখন দিল্লিতে চাকরি পেল, তাহেরপুরের বাড়ি থেকে দিল্লী চলে গেল। বড়দা বাবা-মায়ের সঙ্গে দিল্লী গেল না। বাবা ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশে কাজ করতেন, বদলি হলেন বেলঘরিয়া থানায়। আমার তখন দু’বছর, মেজ বোনের সবেমাত্র জন্ম হয়েছে। এইসময় বাবা আমাদের দুই বোনকে, মা, দাদা, ছোটপিসি আর আমাদের ঠাকুরদাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় থানার কোয়ার্টারে চলে এলেন। বাবার ছিল বদলির চাকরি। ফারাক্কা, মথুরাপুর, নামখানা, মালদা দূরে দূরে পোস্টিং হত। আমরা ছোটবেলায় বাবাকে খুব কমই পেয়েছি। মা-ই ছিল সব। বাবা দাদাকে বলে যেতেন, “খোকন, মাসিকে সব সময় হেল্প করবি। তুই বাড়ির একমাত্র বেটাছেলে।’ বাংলাদেশ থেকে আমার তেরো বছরের মা দিদির সংসারে এসে উঠেছিলেন। পরে জেঠিমা তার দেওরের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিলেন। তাই দাদারা কাকি না বলে মা-কে মাসিই বলত। দাদা ছিল মায়ের ছায়া সহচর। আমাদের শৈশবের স্মৃতি জুড়ে আছে বড়দা, ওরফে খোকনদাদা। পাড়ায় অনেকগুলো পুকুর ছিল। এখনকার মত পুকুর বুজিয়ে বহুতল ওঠার কালচার তখনও আরম্ভ হয়নি। এন-ব্লকের পুকুর, এল-ব্লকের পুকুর, কে-ব্লকের পুকুর এমন সব। কিন্তু আমাদের কাছে তাদের চরিত্র ভিন্ন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি সহস্র বার পড়তে পড়তে তখন আমাদের প্রায় মুখস্থ। একটা পুকুরে লাল শালুক ফুটত। সেটার নাম লালকমল। আরেকটা পুকুরের পাড়ে আমগাছ ছিল। তার সবুজ ছায়ায় পুকুরের জল একটু কালচে নীল বর্ণ দেখাত। ব্যাস, ওটা হয়ে গেল নীলকমল। একটা পুকুরের পাড় থেকে একটা নারকেল গাছ বেঁকে জলের ভিতরে প্রায় সমান্তরাল একটা বসার বেঞ্চের মত হয়েছে, তার গা জড়িয়ে উঠেছে একটা অশ্বত্থ গাছ। দাদাকে বলতাম, “ওই গাছদুটো একসঙ্গে কেমন করে হল রে?” দাদা বলত, “ওদের আগের জন্মে খুব ভাব ছিল। কিন্তু দুজনের দুটো দেশে বিয়ে হয়ে গিয়ে দুজনা দুজনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তখন ওরা খুব কাঁদত। তাই ভগবান ওদের বলল, পরের জন্মে তোমরা একসঙ্গে থাকবে। দ্যাখ না, তাইতো এমন একসঙ্গে আছে দুজনে!” আমরা পারতপক্ষে শুনশান দুপুরে ওই পুকুরপাড়ে যেতাম না, ওটা ছিল ভূত পুকুর। শোবার ঘর থেকে যে পুকুরটা সোজাসুজি দেখা যেত, সেটা ছিল লালকমল। যখন বৃষ্টি পড়ত, জানলায় বসে অপলকে পুকুরে বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতাম। সেই অনুভূতির কোন তুলনা নেই। লোহার গরাদ দেওয়া বড় বড় কাঠের জানলা ছিল, যাতে অনেকখানি পাড় ছিল। আমরা দুই বোন অনায়াসে মুখোমুখি বসতে পারতাম, দুজনেই পা মেলে দিতাম একটু বেঁকা করে, ঠিক যেমন ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে দুজন দুদিকে মাথা রেখে একটু তেরচা করে শোয়, তেমনই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ পুকুরের নিচে রাক্ষসীর ঘরে বন্দিনী এক রাজকন্যা থাকে। কোন না কোনও একদিন তার সঙ্গে ঠিক দেখা হয়ে যাবে। হয়তো সে চুল শুকাতে উপরে আসবে, কিম্বা এমনিই চুপিচুপি একবার পুকুরের উপরে ঘুরতে আসবে, যখন রাক্ষসী থাকবে না। তবে সেই পুকুরটাই ভরাট হয়ে গেল সবচেয়ে আগে। পুকুরটা ছিল একটা পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে। পরে জেনেছি, ওটা ছিল অবন ঠাকুরের ‘গুপ্তনিবাস’। ওটা এখন টেগোর কোর্ট। প্লট করে জমি বিক্রি হল, মা বাবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল, ওখানে একটুকরো জমি কেনার জন্য। বাবা বলত, “আমাদের অত টাকা কই?” যাইহোক, ঠিক ওই পুকুরের মধ্যিখানে যে বাড়িটা হল, সেখানে থাকতে এলেন গোপীনাথ স্যার। তিনি ফিজিক্স পড়াতেন। ইলেভেন-এ সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হওয়ার পরে ওনার কাছে ফিজিক্স পড়তে যেতাম। ততদিনে রাজকন্যার মিথ ভেঙে গেছে। কেবল পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে নৃত্য করত পুকুরের জলে টাপুর টুপুর বৃষ্টির ছবি। বাগানে একটা ঝুপড়িতে বাস করত এক বুড়ো উড়িয়া মালী আর তার বৌ। বৃহস্পতিবার মা ফুল টুল দিয়ে একটু বিশেষ ভাবে ঠাকুরের আসন সাজাত। সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ত। মাসের মধ্যে বিশেষ কোন কোন দিন আমাকে বা বোনকে ঠাকুরের সিংহাসন ফুল দিয়ে সাজিয়ে, জল বাতাসা দিতে হত আর সন্ধ্যাবেলা পাঁচালি পড়তে হত। যে সকালে আসন সাজাবে, সে পাঁচালি পড়া থেকে রেহাই পাবে। তবে দুটোই আমিই ভাল পারতাম। আমি এমনিই পুজো করে দিতাম। কিন্তু বোন পাঁচালি পড়ত পয়সার বিনিময়ে। ছোট থেকেই ও ছিল বেশ চালাক। বাড়িতে বয়স্ক আত্মীয়রা এলে বলত, “বুন্ডি, তোমার মাইঝে মাইয়েডা ভারি বুদ্ধিমতী।” বোনের রেট ছিল চার আনা। যদিও সেই মজুরির পয়সায় হজমি কেনা হলে আমিও ভাগ পেতাম। তবে যেদিন ঝগড়া হত, সেদিন দিত না। সব আগেভাগেই চেটে থুথু মাখিয়ে দিত। দশ পয়সার ফুল কিনতে আমার সঙ্গে রোজ যেত বোন। বিশেষ তিথিতে কুড়ি পয়সা বা চার আনার ফুল কিনলে সঙ্গে একটা মালা ফাউ দিত। মালির বৌকে আমি বাবা ইয়াগার ভারতীয় সংস্করণ বলেই বিশ্বাস করতাম। দূর থেকেই মন্ত্র পড়তে পড়তে যেতাম, “অ্যাই কুঁড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়া!” ঝুপড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত মালীর বৌ, “কি? ফুল্ল নেবে?” কলাপাতায় মুড়ে দু’চারটে জবা, কয়েকটা দোপাটি, বেলপাতা, আর তুলসীপাতা দিয়ে মুড়তে যেতেই আমি চিৎকার করে উঠতাম, “আরে আমের পল্লব দিলে না?” আবার বলতাম, “কটা অপরাজিতা দাও না?” এবার মালী বৌয়ের মুখ কঠিন হয়ে যেত। “দসো পয়সায় কেত্ত ফুল্ল চাই?” ফুলের ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকা মালী বৌকে মনে মনে প্রচণ্ড হিংসা করতাম। ভাবতাম, সম্পূর্ণ বাগানখানা ওরই দখলে। কি ভাগ্য! ভবিষ্যতে একজন মালীকে বিয়ে করার স্বপ্নও দেখতাম।
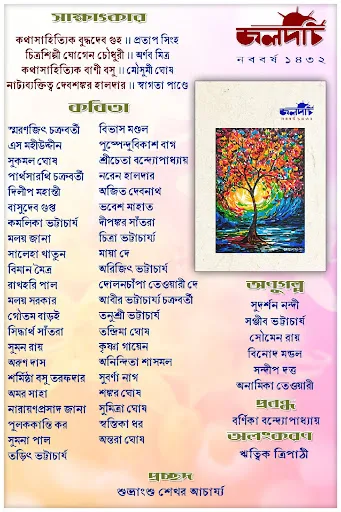



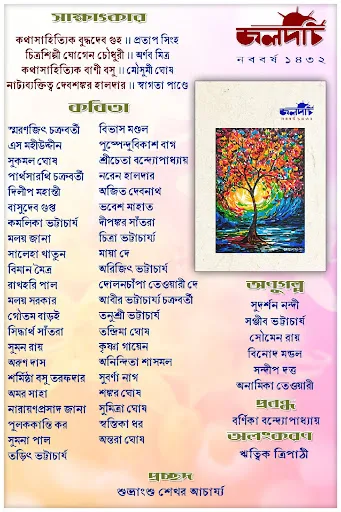












0 Comments