সম্পাদকীয়,
কাকাবাবুকে চেনো তো? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা চরিত্র কাকাবাবু। না চিনলে কাল পীযূষ আঙ্কেলের লেখা পড়ে জেনে নিও। কাকাবাবুর কিন্তু পায়ের সমস্যা ছিল। ক্রাচ নিয়ে চলতেন। তাতে কি? তাতেও উনি ইয়েতি অভিযানে পাহাড়ে চড়েছিলেন। আরে শুধু কি কাকাবাবু এই যে প্যারা অলিম্পিক হচ্ছে টোকিওতে, সেখানে কত কত প্রতিযোগী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে সোনা রূপা ব্রোঞ্জ পেয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করে চলেছে। তবে শুধু প্যারা অলিম্পিক নয় এবারে টোকিও য় আগের বছরে যে অলিম্পিক হবার কথা ছিল তাও হয়েছে। কোভিডের জন্য পিছিয়ে যাওয়া এই অলিম্পিক অনেকের কাছে এক আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। খেলার এমনই মজা। আর এই মজার মজার খেলার কথা এবারের সংখ্যায় শুনিয়েছেন অর্ঘ্য আঙ্কেল আর তোমাদের বন্ধু শ্রেয়সী। মজার ব্যাপার হল খেলার কথা ভাবতে শুরু করলে না ভেবে থাকা যায় না কিন্তু সেটা তো বড়রা বুঝতেই চায় না। সেজন্যই তো সাম্যময় স্যারের কাছে মার খেল। সাম্যময় কে? জানতে হলে পড়তে হবে আবেশ আঙ্কেলের গল্প। এছাড়া আরো কত কত খেলার কথা মনে পড়ছে। এই যেমন ধরো চু কিত কিত। সেটা নিয়ে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষার ছড়া লিখেছেন দেবাশিস আঙ্কেল। এতেও শেষ নয় ছোটোবেলা। যারা খেলা নয় গল্প শুনতে ভালোবাসো তাদের জন্য পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প লিখেছেন সুব্রত আ্যঙ্কেল। আর রঞ্জনা আন্টি পাঠিয়েছেন ছড়া তোমাদের ভালোবাসার স্কুল নিয়ে। এতসবের পরেও যা না বললেই নয় তা ছড়া লিখে বলেছে তোমাদের বন্ধু অনমিতা। সেটা হল, 'পুজো আসছে'। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পুজো এলো বলে। আর আনন্দের কথা হল, বিলম্ব দাদু ফিরে এসেছে ফুলকুসুমপুরের ত্রিপাঠী বাড়িতে। তোমরা এবার জন্মাষ্ঠমীর তালের বড়া আর মালপোয়া খেতে খেতে ছবিগুলো দেখে জানাও এবারের সংখ্যা কেমন লাগলো। -- মৌসুমী ঘোষ।
টোকিওয় ভারতীয় হকির সূর্যোদয়
অর্ঘ্য দে
"আমাদের রক্তে খেলা
খেলার ছলে বিপ্লবী বেশ,
আমরাই কখনো মুখ, কখনো দল... কখনো দেশ”
স্বাধীনতার আগে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ সাল অব্দি বিশ্ব-হকি ছিল একচেটিয়া ভারতের দখলে। এই সময়টা অলিম্পিক-হকি মজে ছিল মেজর ধ্যানচাঁদের হকিস্টিকের জাদুতে। ১৯৩২ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে আমেরিকাকে ফাইনালে ২৪-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার সোনা জেতে ভারত। গোলের এই ব্যবধানের রেকর্ড আজও অক্ষত। স্বাধীনতার পরেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪ সাল অব্দি অলিম্পিকে হকিতে ভারতের সোনার পদক বাঁধা ছিল। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত রুপোর পদক পায়। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকে স্পেনকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে শেষবারের মতো সোনা নিয়ে আসে। সেটি ছিল অষ্টম অলিম্পিক সোনার পদক এবং মোট অলিম্পিক পদকের হিসেবে এগারোতম। জেতার একচেটিয়া অভ্যাসটা এরপর হারিয়ে ফেলে ভারতের হকি দল। তারপর শুরু হল দীর্ঘ পদকশূন্যতা।
এবারের অলিম্পিকের পুল ম্যাচে আমাদের ছেলেদের হকি দলের পারফরমেন্স ছিল চোখে পড়ার মতো। শুরুটা মনপ্রীতরা করেছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতে। তারপর প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭-১ গোলে গুঁড়িয়ে গেছলো আমাদের ছেলেরা। সেই আঘাত সামলে তারপর আবার জয়ে ফিরল। পরের তিনটি ম্যাচে আর আটকানো যায়নি মনপ্রীতদের। এই নজিরবিহীন জয়ের ধারাবাহিকতায় ভারতের ছেলেদের হকি দল একচল্লিশ বছর পরে অলিম্পিকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল।
টোকিও অলিম্পিকে হকির সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের সঙ্গে হেরে সোনার পদকের সোনালি স্বপ্নটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু ব্রোঞ্জ ম্যাচে জার্মানির সঙ্গে হার-না মানা লড়াই দেখে ফাইনালে না উঠতে পারার দুঃখ ভুলে গেলাম। জার্মানির মতো দলকে হারিয়ে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতা আর ফাইনাল জেতা একই ব্যাপার।
এই ম্যাচটা প্রত্যেক হকিপ্রেমী ভারতীয়র মনে থাকবে। ১-৩ এ পিছিয়ে থেকেও খেলায় ফিরে আসা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অপ্রতিরোধ্য মনোভাবে সামান্য সময়ের ব্যবধানে দু’ দুটো পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিল। হার্দিক, সিমরনজিৎদের পরপর দুটো পেনাল্টি কর্নারকে গোলে বদলে দেবার অব্যর্থ প্রচেষ্টা। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই। তখনই যেন জার্মানরা মনের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ল। অবিশ্বাস্য তৃতীয় কোয়ার্টার। আরো দু’টো গোল। এই জমি না-ছাড়ার মানসিকতা নিয়ে যদি বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলতে পারত, ভারত ফাইনালে সোনা পেত, পেতই। অলিম্পিকে পুল ম্যাচের শুরুর দিকে বলেছিলাম ভারতীয় হকির ঐতিহ্য এক দিন না এক দিন ফিরবে, তবে এত তাড়াতাড়ি ফিরবে ভাবতে পারিনি। যাই হোক মনপ্রীত আর তার সঙ্গীদের স্টিকে ভারতীয় হকির একচল্লিশ বছরের পদকের খরা তো কাটল। এও তো কম পাওনা নয়!
আশ্চর্যজনকভাবে এবারের অলম্পিকে ভারতের মেয়েদের হকি দলটিও পৌঁছেছিল সেমিফাইনালে। হকিতে এবারে জোড়া পদকের স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে ছেলেদের দল শেষবারের মতো সোনার পদক নিয়ে দেশে ফিরেছিল, সেই অলিম্পিকেই মেয়েদের দল আয়োজক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ানের কাছে হেরে ৪র্থ হয়ে শেষ তাদের অলিম্পিক সফর। তারপর কেটে গেছে চল্লিশটা বছর। এরপর মেয়েদের দল অলম্পিকে খেলেছে মাত্র দু’বার। গত রিও অলিম্পিকে রানি রামপালের দল শেষ করেছিল ১২ তম দল হিসেবে। এবারে টোকিও অলিম্পিকে একটুর জন্যে ব্রোঞ্জটা ফসকে গেল। তবে শুরুটা রানিদের কিন্তু মোটেই ভালো হয়নি। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই পুল ম্যাচে পরপর তিনটে ম্যাচে হার। পুল ‘এ-র শেষ খেলায় বন্দনার হ্যাটট্রিক গোলে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪–৩ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের পথ পরিষ্কার করেছিল রানিরা। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে আমরা পৌছালাম সেমিফাইনালে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি না তো? রানি, বন্দনা, গুরজিতদের সামনে তখন পদকের হাতছানি। ইতিহাস লেখার সুযোগ। সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ গোলে হেরে বন্ধ হয়ে গেল ফাইনাল ওঠার দরজা। তখনও ব্রোঞ্জের আশা শেষ হয়ে যায়নি। রিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী গ্রেট ব্রিটেনের কাছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেও হেরে গেলাম আমরা। খেলায় তো হার-জিত থাকেই তাই না? প্রতিদিন অভাবের সঙ্গে লড়াই করা রানি, বন্দনা, নেহা, সবিতারা যেভাবে খেলে গেল তাতে ফিরে এল ভারতীয় হকির হারিয়ে যাওয়া সেই ঐতিহ্য, সম্মান। ওরা ব্রোঞ্জ জিতেতে পারেনি, কিন্তু জিতেছে তার থেকেও অনেক বড় কিছু। ওরা জিতেছে অসংখ্য ভারতবাসীর মন, বিশ্বাস। আমরাও পারি, শেষ হয়ে যায়নি আমাদের হকি। এগারো বাঘিনী অ্যাস্ট্রোটার্ফে লিখল অন্য এক ইতিহাস। ওরা মুখ থেকে দল হয়ে দেশ হয়ে উঠল।
সনামণির বে
দেবাশিস দণ্ড
দল দল দলনি
রাঙা মাথায় চিরনি
বর আইসবেক অখনই...
ক্যানে আইসবেক
ক্যানে আইসবেক
ভাগাইন দিব ত্যাখনই।
আম কুড়াতে যা ন খুকু
আম কুড়াতে যা
ডালে চড়ে কঁচকচায়ে
আঞ্জির পাকা খা।
চু কিতকিত চু কিতকিত
চু কিতকিত থা
বাজাইন দে ন হারমনিট
সা রে গা মা পা।
ক্যানে যাবিস জল আইনতে
পদ্মদিঘীর ঘাটে
বইসবি ক্যানে আনাজ লিয়ে
খামড়াবেড়ার হাটে?
সাত দুগুণা চইদ্দ বঠে
দশ দুগুণা কুড়ি
দেইখতে দেইখতে সিঁরায় গেল
খুকুর পেরাইমারি।
পইড়তে পইড়তে ডাগর হ্যল-
হাই ইস্কুল পাশ
ভাল মন্দ বিচার ক্যইরতে
শিখল বারোমাস।
মেয়ামানুষ লয় ব খুকু
মানুষ বঠে আগে
সনামণি লায়েক হঁছে
দেখ ন কেমন লাগে।
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুইটেছে
কদমতলে কে?
কদমতলে উকিলবাবু
সনামণির বে।
মিঠি র সেদিন
সুব্রত দেব
ঘুম ভাঙতেই মিঠি চমকে ওঠে। এ কি! এ আমি
কোথায়? ধূ ধূ করছে মাঠ। দূরে সাদা ওটা কি?
ধপধপে সাদা রং। পাশে একজোড়া পাখনা, ঘাড়ে
সাদা কেশর। ও মা! এ তো পক্ষীরাজ ঘোড়া।
মিঠি একবার ভালো করে চোখ কচলে তাকায়।
না! স্বপ্ন নয়।নিজেই নিজের শরীরে চিমটি কাটে।না -
ও তো জেগেই আছে। তাহলে। তাকে এখানে কে আনলো।
আরে আরে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পাশে বড় সাদা ওটা কি! ঘোড়ার ডিম! তাই তো মনে হচ্ছে। মিঠি যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে। এবার দেখল ডিমটা ধীরে ধীরে ফাটছে আর তা থেকে বেরিয়ে আসছে একটা পক্ষীরাজের ছানা। মিঠির চোখ তো ছানা বড়া।
ঘোড়ার ডিম! তা আবার হয় নাকি। কিন্তু ও তো স্পষ্ট দেখল ডিম ফেটে পক্ষীরাজ ছানা বের হচ্ছে।পক্ষীরাজ ঘোড়া! সে তো দাদাইয়ের কাছে রূপকথার গল্পে শুনেছে।তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে উড়ে চলেছে পক্ষীরাজ ।পিঠে তার রাজকুমার।
ইস! ও যদি অমন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে যেতে পারত ---- যেই না ভাবা অমনি দেখল মাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়া ও তার ছানাটি উড়ে এসে ওর পাশে নামল।কিছু বোঝার আগেই ওকে চাপিয়ে নিল ওর পিঠে।ছানাটি উড়ে চলল পাশে পাশে। এ কি! ওর গায়ে ঝলমল করছে
রাজকুমারীর পোশাক।সাদা কুচি দেওয়া থাক থাক
ফ্রক, রুপোলি ঝালর।মাথার কালো চুলে রুপোলি হেয়ার ব্যান্ড। এমন পোশাক ওকে কে দিল? ওর বন্ধু
রূপাই এর এমন সুন্দর একটা ফ্রক আছে।তবে কি রূপাই -- ভাবা শেষ হয় না , দেখে ওকে নিয়ে পক্ষীরাজ উড়ে চলেছে নীল আকাশের বুকে। পাশ দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে তুলো মেঘের দল। উড়ছে কত পাখি। মিঠি একবার নিচে তাকিয়ে দেখে। - আরে !
ওটা কি! সরু সুতোর মত।নদী নাকি।হ্যাঁ তাই তো।
বাড়ি ঘর গুলোকে ছোট্ট দেখায়।দেখতে দেখতে পক্ষীরাজ ওকে পৌঁছে দেয় মেঘের দেশে ।
মিঠিকে দেখেই মেঘবালিকা ছুট্টে আসে।- এসো
বন্ধু।
মিঠি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে - আমি কোথায় এসেছি?
তুমি তো মেঘের দেশে এসেছ,চলো তোমাকে
ঘুরে ঘুরে আমাদের দেশ দেখাই।
মিঠি তুলোর মত হালকা হয়ে মেঘ বালিকার সাথে ভেসে বেড়ায়। - ওই দেখো চীনের পাঁচিল, ওই দেখো
হিমালয়। ওই দেখো কৈলাশ।
ওই খানে মহাদেব থাকে?
থাকে তো, ওই বরফের পাহাড়ের গুহায়
মহাদেব ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে থাকে।
কি মজা! আচ্ছা ওদের শীত করেনা?
না, ওরা ঠাকুর তো ।
অনেকক্ষণ ঘুরে মিঠি র বেশ খিদে পাচ্ছিল।
মেঘবালিকা বলে - তোমার খিদে পাচ্ছে, দাঁড়াও।বলে
একটা স্বচ্ছ গেলাসে করে এক গেলাস সরবত
মিঠি র দিকে বাড়িয়ে ধরে - এই নাও।
সরবত পান করে মিঠির সারা শরীর মন জুড়িয়ে যায়। - আ! কী সুন্দর।
মিঠি র এবার চোখ জুড়ে ঘুম নামে। তুলো মেঘের নরম বিছানায় কখন যে চোখ লেগে যায়, ও নিজেই
বুঝতে পারে না। ঘুম ভাঙতে দেখে আকাশে ঝিকমিক চিকমিক করছে তারারা। ওর ভালো লাগে
কিন্তু এবার ওর বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকে। ও ভাবে ও দুষ্টুমি করলেই মা বলত - আর দুষ্টুমি করলে তোকে কিন্তু দূরে কোথাও রেখে আসব।
মা কি তাই সকাল বেলা ওকে তেপান্তরের
মাঠে রেখে এসেছিল, আর পক্ষীরাজ ঘোড়া ---
না, এবার ওর চোখে জল এসে যায়।
মেঘবালিকা বলে - এমা তুমি কাঁদছ, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে? আচ্ছা আমি এখনি পক্ষীরাজকে
বলে দিচ্ছি।
ব্যস! কথামাত্র কাজ। পক্ষীরাজ ওকে নিয়ে শন শন
করে উড়ে চলল। দূর থেকে মিঠি ঢাকের আওয়াজ
শুনতে পেল।তারপর হঠাৎ দেখে ও ওদের পাড়ায় পুজো মণ্ডপে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই মা ছুটে
আসে - এতক্ষন কোথায় ছিলি তুই, আমরা চারদিক
খুঁজছি। ও মা! তোকে এত সুন্দর জামাটা কে দিল।
ও মার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছুট্টে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।
ছেলেবেলায়
রঞ্জনা বসু
স্কুল ফেরত পথের বাঁকে
ছেলেবেলা ছবি আঁকে,
অবাক চোখে দেখছিল
তাই তো খুশির বেগ ছিল।
সাত রাজার ধন চতুর্দিকে
সবুজ মনের ঘরটি ভরে
ভাবতে ভাবতে অনেক দূর
ছন্দে নাচে সেই নুপুর
এমন মজা বলব কি তা
সবাই যেন বন্ধু- মিতা
স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে নিয়ে
সময় যেন এগিয়ে চলে
হৃদয় তখন মত্ত মাতাল
আলো হাসির রঙিন সকাল
সেই খুশিটা পথের পাশে
গপ্পোকথা ছড়িয়ে রাখে
রামধনু রঙ আকাশটাকে
জয় করে নেয় ছেলেবেলা
আকাশ আসে হাতের কাছে
তেমন একটি গল্প বলা।
খেলার সময়
আবেশ কুমার দাস
ঘরের পেছনেই মাঠ। জমজমাট বিকেল। টেবিলটা জানলার একদম লাগোয়া নয় ঠিকই। কিন্তু কানে আসেই পঞ্চাশ গ্রাম বল তক্তায় পিটোনোর ঠকাঠক আওয়াজ। আর থেকে থেকেই চেঁচামেচি। ঘরে বসেই টের পাওয়া যায় কী ঘটছে মাঠে। জিকো চিৎকার জুড়েছে। আপ্পুও কম যায় না। সবার উঁচুতে তুলেছে গলা। আরও অনেকের গলা শোনা গেল। নির্ঘাত আউট নিয়ে বচসা। বেচারা আম্পায়ার। ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে কী করে আঙুল তোলে নিজেরই দলের ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে!
একটু দেরিতেই খেলা শুরু হয়েছে আজ। শীতের ছোট বেলা। ঝুপ করে নেমে আসে অন্ধকার। তাও যে খানিক অপেক্ষা করেছিল সবাই, বোঝাই যাচ্ছে। আগের দিন সাঁইত্রিশ রান করা ব্যাটসম্যানকে কে আর রাতারাতি ভুলে যায়!
কী জিজ্ঞেস করছি তখন থেকে, সংবিৎ ফেরে যদুবাবুর হুংকারে, কোথায় পড়ে রয়েছে মন? তিন-তিনবার জিজ্ঞেস করলাম এই নিয়ে, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ কীভাবে সৃষ্টি হয়...
এই রে! তিনবার জিজ্ঞাসা করে ফেলেছেন স্যার! আর সে...
এখুনি হচ্ছিল এক বিপদ।
উত্তরটা যদিও জানাই ছিল। ভূগোল প্রিয় সাবজেক্ট তার। পড়াশুনোতেও ফাঁকি দেয় না মোটেই। ঝামেলাটা আর গড়াল না বেশি দূর। স্যারের মুখে যদিও লেগেই রইল অপ্রসন্ন ভাবটা। কিন্তু চোখে জল আসছিল সন্তুর। বিকেলের আলো থাকতেই যে কেন প্রায়দিনই পা টেনে টেনে উদয় হন যদুবাবু...
ঠকাঠক আওয়াজটা থেমে গিয়েছে হঠাৎই। থেকে থেকে এখন শুধুই হুশহাশ ধ্বনি। উইকেটে লাগতে লাগতেও বারেবারে বেঁচে যাচ্ছে ব্যাটসম্যান। টুটুলের গলা ভেসে এল, ভাই আমাদের বেঙ্কটেশ প্রসাদ...
ওহ। নাটা কুন্তল নেমেছে।
নতুন ছেলেটাকে দেখতে দেখতে তাক লেগে যাচ্ছিল ময়ূখের। কী নাম বলল যেন! সাম্যময়। তা সবার শেষে নেমে তেত্রিশ রানের আনবিটন পার্টনারশিপটাই শুধু নয়, বিরাট বিরাট দুটো ছক্কাও হাঁকিয়েছে সাম্যময়। তাই রানটা পৌঁছল একটু ভদ্রস্থ চেহারায়। এখন বলটাও করছে খাসা। টিংটিঙে চেহারা হলে কী হয়। বেশ জোর আছে বলে। মাঝেমধ্যে আবার আউটসুইং-ও ছাড়ছে। শুরুতে বল দিলেই হত।
সেই কবে থেকে টিভিতে ক্রিকেট দেখছে ময়ূখ। তখন সৌরভ গাঙ্গুলীর শেষের দিক। ইন্ডিয়া খেলা অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিল আগেই। সাম্যময়ের বোলিং অ্যাকশন দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল আইপিএলে গাঙ্গুলীকে বল করতে দেখার কথা। অবিকল অমনি বোলিং গ্রিপ আড়াল করে ছুটে আসা। সিম দেখতে না পাওয়ায় সমস্যা হয় ব্যাটসম্যানের। বাইরের বলটা ধরতে না পেরেই যেমন উইকেট দিয়ে গেল শঙ্খ। শেষ হোক খেলা। জানতে হবে কোথায় বাড়ি সাম্যময়ের। নিয়ম করে আসতে বলবে রোজ। টানা ক’দিন খেলিয়ে দেখে নেবে। তেমন বুঝলে নামিয়ে দেবে তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচে। বুড়োদাও সম্ভবত রাজি হয়েই যাবে।
তালতলার মাঠে অবশ্য রোজই আসে সাম্যময়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। খেয়াল করলেও শুরুতে পাত্তা দেয়নি ময়ূখ। পাত্তা দেওয়ার মতো চেহারাও নয়। শুধু সিড়িঙ্গেমার্কা বলেই নয়। চোখমুখ দেখলেই মনে হয় মুখচোরা। জামাকাপড়ও কেমন আদ্যিকেলে। সস্তার ছিটের কাপড় থেকে দর্জির হাতে বানানো ঢলঢলে প্যান্টজামা। খেলার মাঠে কী করবে এ ছেলে! নেট প্র্যাকটিসের সময় রোজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও তাই মাথা ঘামায়নি ময়ূখ।
কিন্তু গতকাল যা হয়ে গেল!
ইন্দ্রনীলের হাত ফসকে পড়ে যাওয়া ফুলটসে লং অফের উপর দিয়ে সপাটে চালিয়েছিল আলি। ওদিকেই রোজ দাঁড়িয়ে থাকে সাম্যময়। বল তখনও আকাশে। ক’ পা পেছনে ছুটে শূন্যে শরীর ছুঁড়ে দিয়ে যেভাবে একহাতে ক্যাচ নিয়েছিল ছেলেটা, বুড়োদা অবধি তাজ্জব। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। নির্ভুল নিশানায় একেবারে ইন্দ্রনীলের হাতে থ্রো করেছিল অতঃপর লাল বলটা।
তখনই আলাপ। জিজ্ঞাসা করেছিল ময়ূখ, রোজ দেখি এসে দাঁড়িয়ে থাকো। নাম কী গো তোমার?
সাম্যময় হালদার।
কোথায় থাকো?
এদিকেই।
ছোট ছোট উত্তর। যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার থেকে বাড়তি একটা শব্দও খরচা করা নেই। বড্ড লাজুক ছেলে। আবার জিজ্ঞাসা করেছিল ময়ূখ, ক্রিকেট খেলো?
এবার মুচকি হেসেছিল সাম্যময়, খেলতাম। এই বলে নয়...
মানে টেনিস বলে খেলেছে! বিশ্বাস হয়নি ময়ূখের। দু’ দফায় যা খেল দেখাল একেবারে ওস্তাদের মার। মনে হয় লাজুক বলেই চেপে যাচ্ছে নিজের কথা। পাছে ডাকা হয়। তবে জোরাজুরি করলে নেমেই পড়বে হয়তো। খেলাটা তো ভালবাসেই। নইলে স্রেফ নেট প্র্যাকটিস দেখতে রোজ বিকেলে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত!
গতকাল আর বেশি এগোয়নি কথা।
কিন্তু আজই ডেকে নিতে হবে সাম্যময়কে, কে জানত!
তরুণ সংঘর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে দিন পনেরোর মধ্যে শুরু হচ্ছে স্থানীয় লিগের খেলা। নিজেদের মধ্যে একটা ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলার কথা ছিল আজ। কাকু আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তারের বাড়ি ছুটতে হয়েছে ধ্রুবকে। আসতে পারেনি। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল বুড়োদা। তাদের তালতলা ইউনাইটেডের ট্রেনার। তখনই বলেছিল ময়ূখ, ছেলেটা রোজ আসে। কাল দেখে মনে তো হল খেলতে পারবে...
তা ভালই খেলছে সাম্যময়। যদিও ম্যাচটা সম্ভবত হেরেই যাবে ময়ূখরা। রান বিশেষ ওঠেনি। তবে আজকের প্লাস পয়েন্ট হল সাম্যময়কে খুঁজে পাওয়া।
বছরখানেক হল স্থানীয় লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে তালতলা ইউনাইটেড। একেবারে আনকোরা দল। খেটেখুটে দাঁড় করাচ্ছেন বুড়োদা। ক্লাবও বেশিদিনের নয়। মাঠটা যদিও পুরনোই। ক্রিকেট পিচ অবশ্য হালেই হয়েছে। আসলে শেষ ক’ বছরে বেশ বদলে গিয়েছে তালতলা জায়গাটা। তারই পরিণাম তালতলা ইউনাইটেড। মাত্র বছর দশ আগেও এলাকাটা নাকি ছিল পাড়াঘরের মতো। এত ফ্ল্যাটবাড়ি গজিয়ে ওঠেনি। ময়ূখদের লাবণী অ্যাপার্টমেন্টসই যেমন এখনও তিন পুরোয়নি। তা কী ভাগ্যি এত আবাসনের চক্করে মাঠটাই শেষমেশ হাপিস হয়ে যায়নি। তাদের মতো বাইরে থেকে আসা ফ্যামিলিগুলোর ছেলেদের বিকেলে খেলাধুলোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে।
আচমকাই ঘটল ঘটনাটা।
সাম্যময়ের ওভারগুলো দেখেশুনে খেলে দিয়ে উলটো দিক থেকে আর্যর বলে স্কোর এগিয়ে নেওয়ার ছক কষেছিল পিটার আর ইন্দ্রনীল। লুজ বলটা পেয়ে মিড উইকেটের উপর দিয়ে হাঁকিয়েছিল পিটার। মাটি থেকে কম করেও দশ ফুট উঁচু দিয়ে সীমানার বাইরে উড়ে যাচ্ছিল লাল বলটা। ওখানে সাম্যময়কে রেখেছিল ময়ূখ। হঠাৎ সবাই সবিস্ময়ে দেখল সাম্যময়ের ডান হাতটা লম্বায় দীর্ঘ হয়ে অতখানি উঁচুতে উঠে দিব্যি পেয়ে গিয়েছে বলের নাগাল।
নিমেষের স্তব্ধতা। যাকে বলে পিন ড্রপ সাইলেন্স।
পরক্ষণেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে সক্কলের। মাঠময় আওয়াজ ওঠে ‘ভূ... ভূ... ভূত’। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে ব্যাট আর উইকেট। ভণ্ডুল হয়ে যায় খেলা। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যে যেদিকে পারে ছুট লাগায়।
একটু একটু করে তখন আলো কমে আসছে শেষ নভেম্বরের বিকেলের।
ঘরের ভেতর ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকার। মাঠের দিক থেকে চেঁচামেচিও কমে আসছিল। নষ্ট হয়ে গেল পুরো বিকেলটাই। সামনের সপ্তায় ক্যাম্বিস বলের খেলা আছে সাহাপাড়ার সঙ্গে তাদের তালতলার। ফুল হ্যান্ডে খেলা থাকলে সৌরভ গাঙ্গুলীর বোলিং অ্যাকশন নকল করে সে। ইংল্যান্ডে গিয়ে দুটো সেঞ্চুরিই শুধু নয়, জীবনের প্রথম দুই টেস্টে ছ’টা উইকেটও নিয়েছে সৌরভ। বাঁ হাতে ব্যাট করা তো সম্ভব নয়। কাজেই...
সেদিনও কি এমন হবে! খেলার সময় পড়াতে চলে আসবেন না তো যদুবাবু!
অন্যমনস্কতায় খেয়ালই করেনি সে লাইট জ্বালিয়ে দিতে বলেছেন যদুবাবু।
হুঁশ ফিরল আবার এক বাঘা হুংকারে, কথা কানে যায় না! লাইটটা জ্বেলে দিতে বললাম। এত অমনোযোগী কেন...
বলতে বলতেই গাল লক্ষ করে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় কষিয়েছিলেন স্যার। আর ক্ষমা নেই। ভয়ে মাথা নামিয়ে নিতে গিয়েছিল সন্তু। থাপ্পড়টা সপাটে এসে পড়ল কানের পাশে। পরক্ষণেই...
আকাশের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে থেকে দুনিয়ার সব আলো নিভে যেতে টের পেল সে।
আঁতকে উঠেছিলেন যদুবাবুও। ব্যস্ত হয়ে পা টেনে টেনে উঠে এসেছিলেন যত তাড়াতাড়ি পারেন। ব্যাকুল হয়ে ডাকছিলেন অচেতন সন্তুকে ঠেলা দিতে দিতে, সন্তু, কী হল সন্তু... সাম্যময়...

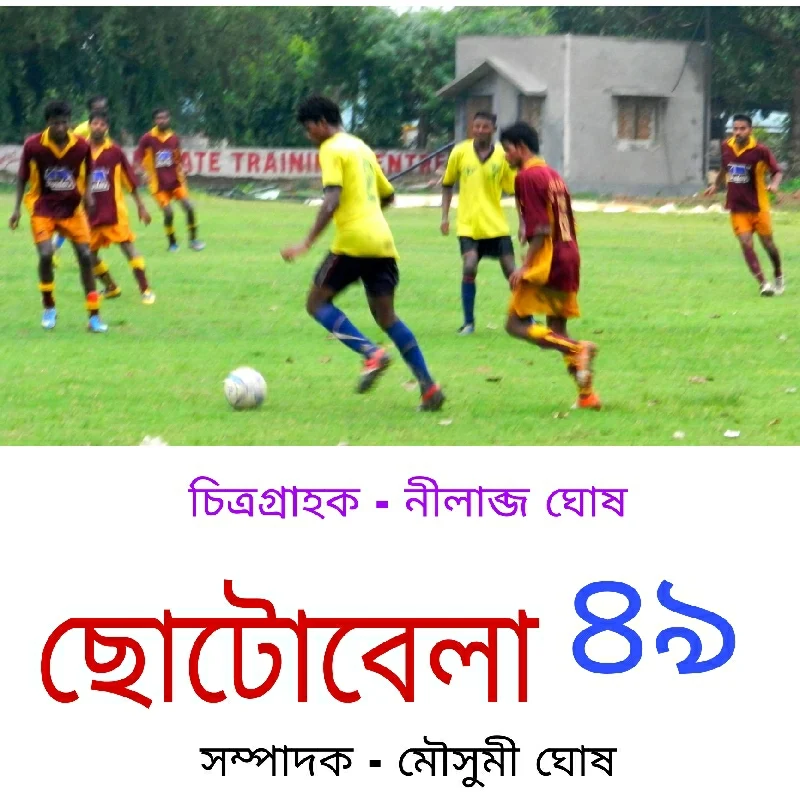





















0 Comments