হাজার বছরের বাংলা গান।। পর্ব-১৭
তু ল সী দা স মা ই তি
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা:
রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানস নির্মাণের কিছুকথা
"এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নুতন নুতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার আঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষনবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।
আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচৰ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার সুবিধা এই হইয়াছিল -অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।" কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন। এই বক্তব্য থেকেই আঁচ পাওয়া যায় ছোটো থেকেই রবীন্দ্রনাথের মননে কিভাবে সংগীত সঞ্চারিত হয়েছিল। কাব্য- নাটক ইত্যাদি শিল্পচর্চার পাশাপাশি সংগীতসাধনাতেও তিনি সমান সময় দিতেন এ কথা বলাই যায়।
ব্রহ্মসংগীতের সূচনা পর্বের আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত প্রসঙ্গে জানতে পেরেছি ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত চর্চার প্রারম্ভকালের কথা। ঠাকুর বাড়িতে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরেই সঙ্গীত চর্চার নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছিল।
এ যাবৎ বিস্তর আলোচনায় পন্ডিতগণ বলেছেন ঠাকুরবাড়ির এই পর্যায়টি বাংলা গানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তৎকালীন জমিদার বাড়িগুলির অধিকাংশ গানের জলসায় বাঈজী নাচ ও চটুল গানের একটা রেওয়াজ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই এই প্রকার নাচ গানের সংস্কৃতি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তে একটা পরিশীলিত রুচিশীল সঙ্গীত সংস্কৃতির অঙ্গন হয়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ি। দেবেন্দ্রনাথ ও তার পুত্রগণ সহ বাড়ির অন্যান্যদের সংগীত প্রতিভার উজ্জ্বলতায় মুখর হয়ে উঠল বাংলার এই সংগীতকেন্দ্র। ব্রহ্মসঙ্গীতের চর্চা প্রাথমিকভাবে অধিক গুরুত্ব পেলেও সার্বিক সংগীত চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। মানবিক অনুভবের সাহিত্য- সংগীত- চিত্রকলা সহ বিবিধ শিল্প -সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হয়ে ওঠার পর্যায়েই এই নব নব সংগীতের সৃষ্টি বাংলা সংগীতিক ইতিহাসে একটা নবজাগরণ। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এক বৃহৎ সংগীতবিদ হয়ে ওঠার এও এক উৎসমুখ। ঠাকুরবাড়ির সমস্ত সংগীত পর্বটি সময়কাল হিসেবে ছোটো হলেও গভীরতায় বৃত্ততর তাৎপর্যের স্মারক।
ঠাকুর বাড়ির সংগীত আয়োজনের ক্ষেত্রে দুটি দিক। এক. ঠাকুর বাড়ির সংগীত অতিথি সহ বাইরের সঙ্গীতজ্ঞদের গান। দুই. ঠাকুরপরিবারের সদস্যদের নিজস্ব সংগীত। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠা, ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসবকে কেন্দ্র করে বাইরের সংগীত শিল্পীদের ঠাকুরবাড়িতে গান ছাড়াও ঠাকুরবাড়িতে বাইরের ওস্তাদ ও শিক্ষকদের রেখে পরিবারের সদস্যদের গান শেখানোর ব্যবস্থা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঠাকুর বাড়িতে যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সহ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীত শিল্পীগণ নিয়মিত যাতায়াত করতেন। যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তো ঠাকুরবাড়িতে সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নদীয়ার বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, চন্দ্রকোনার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সগীত-ব্যক্তিত্ব ঠাকুরপরিবারে সংগীত শিক্ষক হিসেবে বাড়ি আলোকিত করেন। এছাড়া ঠাকুরবাড়িতে "হিন্দু মুসলমান উস্তাদদের বসতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর….. ….বরোদা, গোয়ালিয়র, অযোধ্যা, দিল্লি, আগ্রা, মোরদাবাদ ও অন্যান্য দেশ থেকে সংগীতশিল্পীরা আশ্রয় নিতেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।" বলা বাহুল্য, এসব শোনা বা দেখার সুযোগ হয়েছিল বালক রবীন্দ্রনাথের।
রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু জায়গায় বলেছেন তিনি বিধিবদ্ধভাবে গান শেখেননি। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা বলতেই হয়। আসলে জ্যোতিদাদারা নাড়া বেঁধে যে পদ্ধতিতে গুরপরম্পরাভাবে নিবিড় শিক্ষায় যুক্ত হয়েছিলেন সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ শেখেনি। ঠাকুরবাড়ির সংগীত পরিবেশে তাঁর শিক্ষা ছিল অনেক বেশি স্বশিক্ষা।
বলা হয়ে থাকে বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রকৃত অর্থে রবিঠাকুরের প্রথম সংগীতগুরু। তিনি নিজে তাঁর আত্মজীবনী 'ছেলেবেলা' তে বিষ্ণু চক্রবর্তীর সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। জানা যায় তিনি উত্তর ভারতীয় রীতির উচ্চাঙ্গ সংগীত- ধ্রুপদ,ধামার,খেয়াল টপ্পা ও ঠুমরি ইত্যাদি যেমন গাইতেন তেমনি বাঙালির নিজস্ব রীতির নানা অঙ্গের গানও গাইতেন। তাঁর কন্ঠসৌকর্য ও সাবলীল গায়নরীতি কবিকে মুগ্ধ করতো।
শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন ঠাকুর বাড়ির আর একজন সংগীতশিক্ষক। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভক্তবন্ধু'। একসাথে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রাণবন্তভাবে তিনি সংগীত পরিবেশন করতেন। একটা অদ্ভুত আবেগময় আবেদন ছিল তার সঙ্গীত গায়নে। তিনি প্রকৃতভাবেই সংগীত-রসিক ছিলেন। আনন্দ-হাসি ও স্ফূর্তিকে তিনি গানের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধীরে এসব সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর গুনাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসাসূচক অনেক কথা বলেছেন। 'জীবনস্মৃতি' তে তিনি বলেছেন "গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকন্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান - 'ম্যায় ছোঁড়ো ব্রজ কি বাঁসুরী।' ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক ''ম্যায় ছোঁড়ো'- সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন এবং অশান্ত ভাবে সেইটি ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন ঠেলা দিয়া উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"
যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংগীত গুরু ছিলেন না তবে পরোক্ষভাবে রবির গানে তাঁর সংগীত সাধনার বৃহৎ প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই তার উল্লেখ আছে। যদুভট্ট-এর সংগীতগুণ ও তাঁর স্বকীয়তার নানা দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় বলেছেন। অনেকে মনে করে যদুভট্টের গানের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথে অধিকভাবে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ গানের অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর গানে বিষ্ণুপুর ঘরানার গানের মতো করে আঙ্গিক নির্মিত হয়েছিল তার অনেকটাই যদুভট্ট-এর প্রভাবেই। তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গ্রন্থে যত কথা বলেছেন আর কারো সম্পর্কে এমন বলেছেন বলে মনে হয় না। এক জায়গায় তিনি বলেছেন- " ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম,- গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্যাদায় ছিল,কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল ঠোকাঠুকি করতো না। ..তিনিই বিখ্যাত যদুভট্ট।...যখন তিনি আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসতো তাঁর কাছে শিখতে, কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিনীর আলাপ। বাংলাদেশে এরকম উস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর গানে একটি originality ছিল,- যাকে আমি বলি স্বকীয়তা"।
ঠাকুরবাড়ির সংগীত শিক্ষক ছাড়াও নানাভাবে যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে জ্যোতিদাদার স্থান সবার ওপরে। সবচেয়ে বেশি সংগীতসঙ্গ পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই। গান রচনা ও সেই গান সুর দিয়ে পরিবেশন করা এসব প্রাথমিকভাবে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। জ্যোতিরিন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় সঙ্গীতসমাজ (১২৯৯)' রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ বাংলা গান অনুশীলনের পরিবেশ পেয়েছিলেন এইখানে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও ব্রহ্মসংগীত ছাড়াও অন্যান্য গানেও অনুরাগী ছিলেন। যাত্রা, কথকতা, কবিগান,কীর্তন, বাউল,প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার গান গাওয়ার পরিবেশ তিনি তৈরি করেছিলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্পর্শ বেশি করে পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এসব নীরবে সঞ্চারিত হয়েছিল,
দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানসে প্রবেশ করেছিল বলা যায়। এক্ষেত্রে দাদা অফুরান স্নেহ দিয়ে ভাইয়ের প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের সংগীতপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গ দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র ঠাকুর সহ প্রায় সকলেই সংগীত অনুরাগী ও সহযোগী ছিলেন। ঠাকুর বাড়িতে মেয়েদের সংগীতচর্চাও শুরু হয়েছিল পূর্ণমাত্রায়।
এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত স্রষ্টা হয়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথের গান আসলে 'এক বিবর্তিত পূর্ণাঙ্গ সংগীত'। আর এই নীরব সঞ্চরণ-এর মধ্যে যে বহুমাত্রিকতা আছে তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটা দীর্ঘ সময়ের বাঙালির নিজস্ব সংগীত চর্চার আবহ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলাগানের নির্মাতা তিনি। পূর্ববর্তী বাঙালির সংগীত চর্চার সবটুকুর একটা নির্যাস খুঁজে পাই তাঁর গানে। আর এখানেই তাঁর গানের মহিমা। সমগ্র বিশ্ব জুড়েই একারণেই তাঁর গানের সমাদর।
(চলবে)




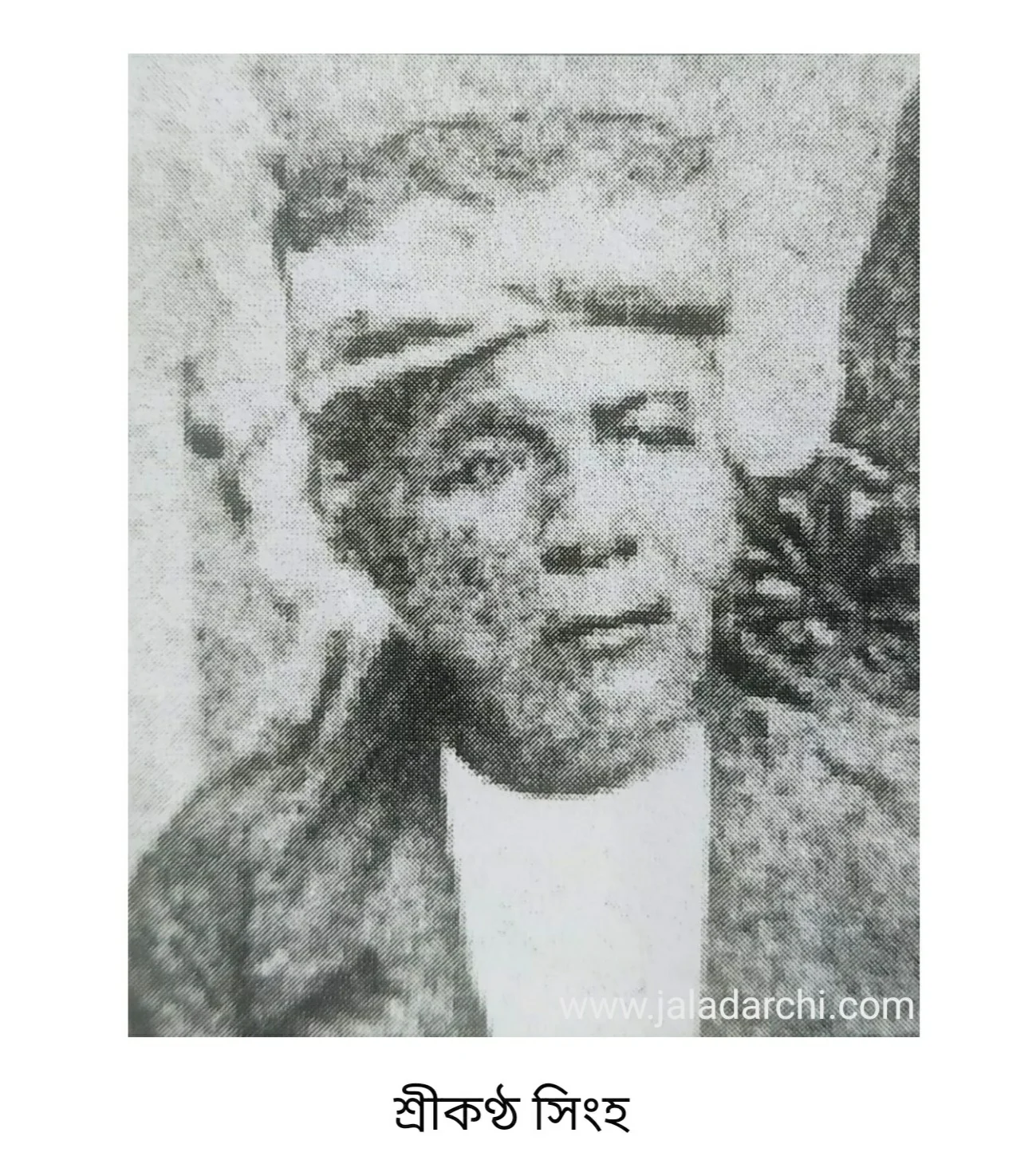













0 Comments