পুলককান্তি কর
ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ভদ্রলোকে বিয়ে করে! দিনরাত খালি “এটা কোরো না ওটা কোরো না; হা ভগবান, কাকে নিয়ে ঘর করি” ইত্যাদি কাঁহাতক আর মানুষের ভালো লাগে। আগে তাও শুধু বউ এর কিচিরমিচির শুনলে হয়ে যেত। ইদানীং আবার ছেলেও লায়েক হয়েছেন। তাঁর বিচারবুদ্ধি কখনোসখনো মায়ের থেকেও তীক্ষ্ণ। সুতরাং জোড়াফলার থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে মেজাজ আর অরবিন্দবাবুর কন্ট্রোলে থাকে না। ছেলে কিছু একটা বলতে যেতেই চোখ দিয়ে যেন আগুন ঢেলে দিলেন তিনি। তবে কিনা ঢোঁড়া সাপ কামড়ালেও গায়ে বিষ ওঠে না; অতএব এরপরও ছেলে গজগজ করতেই থাকল। তাই দেখে কান-মাথা ঝাঁ ঝা করে উঠল তাঁর। গায়ে মাথায় জল দিতে যেই বাথরুমে ঢুকলেন, অমনি ঝনঝন করে উঠলেন নীপা, ‘এই যে, দিনে ক’বার স্নান হবে শুনি ? সকালে তো একদফা হয়েছে।‘
“মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো। তোমাদের সাথে ঘর করতে হলে, সারাদিন পুকুরে ডুবে থাকলেও শরীর জুড়োবে না।”
“পুকুরে কেন, বরফগলা জলে গিয়ে ডুবে থাকো না, কে বারণ করছে? শুধু হাঁচি-কাশি না হলেই হলো। একবার খালি হেঁচে দ্যাখো?”
সবে বালতিতে জল ভরা শুরু করেছিলেন অরবিন্দবাবু, এমন চেঁচামেচির চোটে শুধু চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। রাম রাম! তিনি কি জেলের কয়েদি? দেখলেন টেবিলে এখনও খাবার দেননি নীপা। আচমকা হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, “খাবার কি টিফিন কৌটোয় বেঁধে দেবে নাকি?”
‘’ঠিক এসে যাবে।”
“কথার ছিরি দ্যাখো! সবসময় যেন তেড়ে আসছে। জন্মের সময় কি মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিল তোমায়?
“কাকে আর জিজ্ঞেস করব? আমার তো আর মা-বাবা বেঁচে নেই। তুমি বরং তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কোরো, তোমার মুখে কি পড়েছিল।”
অরবিন্দবাবু আর কথা বাড়ালেন না৷ চুপ করে নাকেমুখে গুঁজে দিতে লাগলেন তিনি৷ আর একটু দেরি হলেই অফিসে লেট হয়ে যাবে তাঁর। তিনি বেরিয়ে যেতেই ছেলেকে আড়চোখে দেখলেন নীপা। এখনও গুম মেরে বসে আছে। গলাটা যতটা সম্ভব নরম করে বললেন, “আয় তপু, জলখাবারটা খেয়ে নে৷
“এখন খাবো না মা, খিদে নেই।”
“খিদে নেই বললে কি হয় বাবা? পিত্তি পড়ে যাবে। আর তোর বাবার কথা অত ধরিস না।”
“আমি কী এমন অন্যায় কথা বলেছি বলো? বাবা-জ্যাঠাদের মধ্যে জায়গাজমি যখন ভাগ হয়েই গেছে, বাস্তু জমিতে আমাদের অংশে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আজকে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক আছে, ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা মিটে যাবে। বাবা-জ্যাঠার অবর্তমানে এই নিয়ে চুলোচুলি হলে কে মেটাবে? আইন-আদালত মানেই এককাঁড়ি টাকা খরচ আর ঝঞ্ঝাট। যত্তসব !”
“এই নিয়ে তুই আর মাথা গরম করিস না। আমি তোর বাবাকে বুঝিয়ে বলব’খন৷।'
“তুমি বললেই কি শুনবে? দেখলে তো আমায় কেমন তেড়ে এল। বলেই দিল – ‘এই সম্পত্তি আমার বাবা আমার নামে দিয়েছে। আমি যদি তোর নামে কখনও লিখে দিই, তখন এই নিয়ে কথা বলতে আসবি। এখন এইসব নিয়ে তোর কোনও কথাই শুনব না।‘ ভালো কথা বলতে গেলেও দোষ !”
“ছাড় তো তোর বাবার কথা। আজকাল অল্পেই ওর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। দেখিস না, সবসময় কেমন তেড়ে তেড়ে আসে, রাগ দেখায়।”
“তা যেখানে রাগ দেখানোর কথা, সেখানে দেখাতে বলো না! খালি আমাদের উপরেই তড়পানি! জ্যাঠারা যে দিন দিন আমাদের বাস্তুর দিকটা আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে, তাদের কিছু বলছে? গতবার যখন গেলাম, তখন দেখি আমাদের অংশে শাকের মাচা বানিয়েছে, আমগাছ পুঁতেছে। এবার তো দেখি আস্ত একটা তুলসী মণ্ডপ বানিয়ে ফেলেছে। তা আমাদের জায়গাটাও যখন ওরা ভোগ করছে, তাহলে আমাদের অন্য কোনওভাবে কমপেনসেট করুক।”
“কীভাবে করবে?”
‘’যেমন ধরো, আমাদের খরচার জন্য যতটা চাল পাঠায়, আরও বেশী করে পাঠাক!
“যা পাঠায়, তাই তো বেশি হয়ে যায়। আরও বেশি দিলে কি তুই বিক্রি করতে যাবি?”
“তাহলে টাকা ধরে দিক”
“একথা কে বলতে যাবে?”
“কেন, বাবা বলবে।”
“তাহলেই হয়েছে। জানিসই তো, তোর বাবা কাউকে কটু কথা বলতে পারে না৷ একবার কী হয়েছিল জানিস? গল্পটা তোর বাবার মুখ থেকেই শোনা। তখন ও এইট-নাইনে পড়ে। একদিন একজন লোক জুতোতে পটি পাড়িয়ে বাড়িতে উঠে আসছিল। ও দেখছে লোকটা ওই জুতো নিয়ে উঠোনে উঠে আসছে, তবু বলতে পারেনি, জুতোটা ছেড়ে আসুন। লোকটা সারা উঠোন নোংরা করে দিয়ে গেল। ও চলে যেতে আবার বাবাকেই জলের বালতি এনে সব পরিষ্কার করতে হলো।”
“বাবা পরিষ্কার করল কেন? বাড়িতে লোকজন ছিল না?”
“তোর বাবা একাই বাড়িতে ছিল।”
“জিজ্ঞাসা করোনি, দেখা সত্ত্বেও বাবা লোকটাকে বাড়িতে উঠতে দিল কেন?”
“করেছিলাম তো। তা কী বলল জানিস? বলল, বললে নাকি লোকটা বড় লজ্জা পেত। সেই লোক বাপ-দাদার মুখে এতবড় কথা কী করে বলবে বল?”
“তাহলেই বোঝো৷। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এই সম্পত্তিটা পুরোটাই টুবাইদা আর বুবাইয়ের গর্ভে যাবে। আমাদের শুধু বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।”
“ঠিক আছে। তুই এখন কলেজ যা। আমি সময়-সুযোগ বুঝে এই নিয়ে বাবার সাথে কথা বলব।”
তপু জলখাবার খেয়ে কলেজে চলে গেল। দুপুরের খাওয়া ও কলেজের হস্টেলে খায়। ও যেতেই নীপা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। আজকাল অরবিন্দবাবুর খুব রাগ হয়েছে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। ডাক্তার গুপ্তকে ব্যাপারটা বলতে হবে। সুগার-টুগার বাড়ল নাকি কে জানে? রক্ত পরীক্ষার কথা বললে তো আবার খেপে যাবে। গত সপ্তাহে প্রেসারটা মাপা হলো। মোটামুটি নর্মাল। হোমিওপ্যাথিতে নাকি রাগ কমানোর ওষুধ আছে? মামাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।
সন্ধেবেলায় অরবিন্দ বাড়ি ফিরে দেখলেন, নীপা রান্নাঘরে। রাতের রান্নাবান্না করছেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে৷ চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ, তবু মায়াময়। অন্য দিন হলে অরবিন্দ কিছু না কিছু হাল্কা রসিকতা করতেন। আজ আর ওই পথে হাঁটলেন না। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে সোফাতে গিয়ে বসলেন। ওঁকে দেখে চায়ের জল চড়িয়ে দিলেন নীপা। তপুর পড়ার ঘর অন্ধকার। লাটসাহেব এখনও বোধহয় ক্লাবঘরে ক্যারাম পিটোচ্ছেন। অরবিন্দ কিছুতেই সকালের ঘটনাটা ভুলতে পারছেন না। এত বিষয়বুদ্ধি কোথেকে পেল ছেলেটা? আড়চোখে একবার তাকালেন নীপার দিকে। নির্ঘাত ওর বাড়ি থেকেই এই জিনটা এসেছে। ওর বাবার বিষয়-আশয়ের একটা বাই ছিল। কথাটা মনে আসতেই জোর করে ঢোক গিললেন তিনি। একথা ভুল করেও যদি কথাচ্ছলে বেরিয়ে পড়ে, কপালে দুঃখ আছে তাঁর। নীপা অমনি বলবেন, “নিজের বাড়িটা ভুলে যাচ্ছো কেন? তোমার দাদা কি কম মেরে খাচ্ছেন?” এসব ভাবতেও কষ্ট হয় তাঁর। রাতের খাওয়া শেষ হলে আগেভাগে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি, যাতে নীপা অন্তত আজ রাতে তাঁর মগজধোলাই করার সুযোগ না পান। কিন্তু ঘুমও আজ তাঁর সাথে শত্রুতা করে বসল। চোখ বুজে ঘুমের ভান করলেন বটে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে নীপা যখন শুতে এলেন, তাঁর কাছে বিষয়টা গোপন রইল না৷ মুদু স্বরে বললেন, “কী গো, ঘুমোওনি যে বড়! এসো, চুলে একটু বিলি কেটে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে যাও। নইলে শরীর খারাপ করবে।'
“ঘুম আসছে না।”
“মিছিমিছি সকালের কথা নিয়ে ভাবছ কেন? এখনই তো তোমাকে কিছু বলতে হচ্ছে না৷ পরের কথা পরে ভাবা যাবে৷”
“আমি ওকথা ভাবছি না নীপু। আমি ভাবছি তপুর কথা৷ আমি তো কখনও ওকে কুশিক্ষা দিই না। ওর মধ্যে এত হিংসা এল কী করে? এই বয়সে এত বিষয়বুদ্ধি ?”
“কিন্তু ও তো অন্যায় কিছু বলেনি।”
“অন্যায় বলেনি? তুমিও ওকে আস্কারা দিচ্ছ? সকালে বরং তোমার ওকে শাসন করা উচিত ছিল। আমরা ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। যত টাকাই খরচা হোক না কেন, ওকে দাঁড় করিয়ে যাব। বিষয়-আশয় নিয়ে ওর এত ভাবনা কেন? তুমি দেখো, ওর জন্য আমি কিচ্ছু রেখে যাব না। সব উড়িয়ে দিয়ে যাব।”
“তুমি সবসময় এই কথা বলো কেন বলো দেখি?” বেশ রাগত স্বরে বললেন নীপা। “ইদানীং দেখছি তুমি প্রায়ই এই কথা বলো। ছেলে এখন বড় হচ্ছে। একথা শুনলে ওর রাগ হবে না ?”
“রাগ কেন হবে? আমার সম্পত্তি আমি ওকে নাও দিতে পারি।”
“তবে জন্ম দিয়েছ কেন?”
‘’জন্ম দিয়েছি বলে, খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি। যাতে সুশিক্ষা পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে চেষ্টাও করবো। মাথার উপর ছাদ করে দিয়েছি। সারা জীবন সে ছেলেপুলে নিয়ে কী খাবে, তার ব্যবস্থও আমাকে করে যেতে হবে?
এবার আর রাগ বাগ মানতে চাইল না নীপার। তাঁর এখন মেনোপোজাল সিনড্রোম চলছে। কারণে-অকারণে তাঁরও আজকাল রাগ হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু বলেছেন, এমনটা নাকি আরও তিন-চার বছর চলবে। বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ করলেন তিনি৷ এখন উনিও রেগে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে৷ শুধু বললেন, “সব বাবা-মাই তার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের সুরক্ষার কথা ভেবে সাধ্য মতো কিছু রেখে যায়। আমরাও রেখে যাব, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। তুমি খামোখা এ নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না৷ কত ওড়াতে পারো, ওড়াও না! তোমাকে তো কেউ কঞ্জুসি করে জমাতে বলছে না৷”
“আচ্ছ, একটা কথা তুমিই ভেবে দ্যাখো। এই ফ্ল্যাটটা প্রায় তেরোশো স্কোয়ার ফিট। শোভাবাজার এরিয়ায় এত বড় ফ্ল্যাট -- বুঝতেই পারছ, ভালো দাম। বারাসাতে বড় একটা বাগানবাড়ি কিনে রেখেছি। সেখানেই আমরা থাকতে পারি না। এরপরও গ্রামের ওই বাড়ি নিয়ে এত মাথাব্যথার কী কারণ? বছরে নমো নমো করে এক-দু'দিন যাই। কোনও বছর লক্ষ্মীপুজোয়, কখনও বা শীতকালে, পিঠে খেতে। বছরের দু'একদিনের সেই আনন্দটুকু মাথায় রাখো না কেন? দাদারা যদি ওই জায়গাটা ভোগই করে, ক্ষতিটা কী?”
“দ্যাখো, তুমি জানো আমি কখনও যেচে কারও অনিষ্ট করি না৷ কারও এক আনা মেরে নেওয়ারও আমার প্রবৃত্তি নেই। যে জিনিস তোমার বাবা তোমাকে দিয়েছেন, সেখানে আস্তে আস্তে দাদারা দখল জমিয়ে নিচ্ছেন -- সেটা তো ন্যায়ের কথা নয়। অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করবে না? চুপ করে থাকলে সবাই ঠকিয়ে খাবে। তুমি যে অন্যায়টা ধরতে পেরেছো, সেটাও তো অন্যকে বোঝানো দরকার।”
“প্লিজ নীপা, এভাবে বলো না৷ তোমরা যেন ধরেই নিয়েছ দাদা আমাকে ঠকিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। বাবা বেঁচে আছেন। তাঁর সামনে তাঁরই জমিতে যদি তুলসী মণ্ডপ তৈরি হয় বা গাছ লাগানো হয়, এতে অন্যায়টা কী? আমরা হলে হয়তো আমরাও করতাম। আর তাছাড়া দাদা আমাকে ঠকাবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না৷”
“দাদা মানে তো আর আগের দাদা নন। দাদা মানে দাদা, বৌদি ও তাঁর পরিবার। এই দ্যাখো না, আমি তোমার সাথে কথা বলছি, তুমি চিত হয়ে শুয়ে আছো; কথাগুলো একান দিয়ে ঢোকাচ্ছ ওকান দিয়ে বের করে দিচ্ছ। তোমার বউদিও দাদা শুতে এলে এমনি কান-ফুসফুস দেয়। তবে দাদা যখন পাশ ফিরে শোয়, দিদি তখনই কথাটা বলে। উপরের কান দিয়ে কথাটা ঢোকে, নীচেরটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না-- এই যা তফাত।” নীপা মজা করলেন।
আজ আর মজা নেওয়ার মুডে নেই অরবিন্দ। তিনি সিরিয়াস গলায় বললেন, “এটাই তো সমস্যা। আমাদের ভায়ে ভায়ে ব্যাপার। তোমরা মাঝখানে এসে নাক গলাচ্ছ কেন?”
‘’আমরা গলাব না তো কে গলাবে? এখন তুমি-আমি বলে তো কিছু নেই। এখন আমরা। এটা ভাবতে পারো না, আমরা একটা ইউনিট ?”
“সেরকম আমরা, দাদারা, বাবা -- সবাই মিলে একটা পরিবার, একটা ইউনিট, এটাই বা ভাবতে পারো না কেন?”
“পারি না, কারণ সেটা নয় বলে। সত্যি বলো তো, তুমি নিজে ভাবো?”
অরবিন্দ চুপ করে রইলেন। সত্যিই, তাঁদের সবার মধ্যে মৌখিক সুসম্পর্ক হয়তো আছে, কিন্তু আগেকার মতো একান্নবর্তী পরিবারের ধর্ম কি তাঁরা পালন করেন? যে যার মতো নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। দাদার বড় ছেলে টুবাই ব্যাঙ্কে চাকরি করে; শহরে থাকে। ছোট ছেলে বুবাই বিদেশ যাচ্ছে। তার ছেলেও কোথায় থাকবে ঠিক নেই। শুধু দাদা আছেন বলে সন্ধেবেলায় অন্তত বাস্তুভিটেয় শাঁখটুকু বাজে। বাবারও সেবাযত্ন হয়। দেশের বাড়িতে তাঁদের দুই ভাইয়ের নামে যে জমিজমা আছে, তাদের চাষবাস দাদাই দেখাশোনা করেন। তাঁদের বছরের চালটা বাড়ি থেকে আসে। কেউ ওখান থেকে এলে দাদারা কিছু আনাজপাতিও পাঠিয়ে দেন৷ তবে ধান-চাল বা আনাজ যা উদ্বৃত্ত হয়, সব বিক্রি হয় নিশ্চয়ই। অরবিন্দ সে সব খবর রাখেন না। অবশ্য স্ত্রী আর ছেলের বক্তব্য, ওই টাকা সব দাদাই ভোগ করেন৷ তিনি অনেকবার মিনমিন করার চেষ্টা করেছেন, বাবার একটা খরচা আছে, তাঁর ওষুধপত্র আছে, বাবার লোক-লৌকিকতা বা গুরুদেবের আশ্রমের জন্য দান -- এসবগুলো কি এমনি এমনি হয়? শ্রোতারা এই যুক্তি উপলব্ধি করেছেন, এমন প্রমাণ অবশ্য মেলেনি। একটু পরে অরবিন্দ বললেন, “দ্যাখো নীপু, যদি ধরেই নিই তোমাদের কথাই ঠিক, তবেও কি আমাদের কিছু আসবে যাবে? দাদারা যদি আমার অংশ থেকে কিছু দখলও নেয়, কত নেবে ? দু'কাঠা ? পাঁচ কাঠা ? এর বেশি তো নয়। ওখানে পাঁচ কাঠার কত আর দাম? এক লাখ? দু'লাখ? যদি ওরা নিয়ে শান্তি পায়, পাক না। এই ক’টা টাকার জন্য তপুটা ইতরামি শিখছে, তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছ, আমাকে মানসিক অশান্তি পোয়াতে হচ্ছে -- এসব কি ভালো? আজ আমার ঘুম হবে না, এসব ভেবে ভেবে প্রেসার বাড়বে, সবথেকে বড় কথা, এসব ব্যাপার বাবা বা দাদাকে বলতে গেলে আমাকে কী পরিমাণ ছোট হয়ে যেতে হবে -- সেসব একবার ভেবে দেখবে না? আমি তো কম রোজগার করি না! তোমাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যেরও কোনও ত্রুটি রাখিনি। আমার মানসিক শান্তি বা ইচ্ছের থেকেও দু'লাখ টাকা বেশি দামী?’’
“ঠিক আছে, তোমাকে ওদের কিছু বলতে হবে না। কিন্তু স্বীকার তো করো, ওরা অন্যায় করছে।”
“আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে তোমার কী লাভ নীপা? তাহলেই তুমি শান্তি পাবে? যে সব কুটিলতা ভাবতেও কষ্ট হয় আমার, তাই তুমি আমার মুখ দিয়ে কেন বলিয়ে নিতে চাও?
‘’ঠিক আছে, তোমায় কিছু বলতে হবে না। এখন ঘুমোও।”
নীপা অরবিন্দের বাহুর উপর মাথা রেখে আস্তে আস্তে তাঁর গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার দৌড় বিছানা পর্যন্ত। সুতরাং, তাঁদের আজকের মতো সন্ধি হয়ে গেল।
সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীরটা বেশ হাল্কা লাগল অরবিন্দবাবুর। প্রাতঃকৃত্য আর স্নান সেরে যখন বসার ঘরে এলেন, গতদিনের কোনও গ্লানি আর পীড়া দিল না তাঁকে। তপু উঠে পেপার চিবোচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ রে, তোর কলেজের টিউশান ফি জমা দিয়েছিস?”
“না।”
“না মানে? আজ পনেরো দিন হলো তোর মাকে টাকা দিয়ে রেখেছি, তোকেও বলে দিয়েছি, এতদিনে কলেজের পাশের ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফট বানিয়ে দিতে পারলি না?”
“সময় পাইনি”
“তা, লাস্ট ডেট কবে?”
“কাল বোধহয়।”
“বোধহয় মানে? সে হুঁশও নেই ? ফাইন হলে ভরবে কে শুনি ?” রক্ত আবার চড়চড় করে উঠতে লাগল মাথায়।
গোলমাল শুনে নীপা বললেন, “ঠিক আছে, আর চেঁচাতে হবে না। আমি গিয়ে জমা করে দেব না হয়।”
রাগে গরগর করতে করতে চা খেয়ে বাজার গেলেন অরবিন্দ। আজ তিনি সি. এল নিয়েছেন৷ ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিসের কাজ অনেক জমে আছে। তাছাড়া ঘরের দরজা-জানলায় রঙ করার মিস্ত্রি লাগবে পরশু থেকে। সব জিনিসপত্রও সেজন্য গুছিয়ে রাখা দরকার। ব্যাঙ্কে যখন যাবেনই, তপুর ফিস্ টাও জমা করে দেবেন। কলেজের টিউশান ফি ওদের অনেক। প্রাইভেট কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে সে। জয়েন্টে ওর যা র্যাঙ্ক ছিল, ভালো কলেজে ভালো সাবজেক্ট পেত না সে। নীপা চেয়েছিলেন তপু পরের বছর আর একবার জয়েন্টে বসুক। কিন্তু একটা বছর নষ্ট হোক, অরবিন্দ চাননি। কিছুটা কৃচ্ছসাধন করেও ছেলেকে তিনি ভালো প্রাইভেট কলেজে ভর্তি করিয়েছেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেন কী ! সব কিছু কি বাবা-মাকেই করে দিতে হবে? কই, তাঁরা যখন ছোট ছিলেন, তাঁরা তো বাবা-মা’র উপর সব চাপিয়ে দিতেন না! বাবা একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন। কতই বা মাইনে ছিল তাঁর। তিনি, দাদা দু'জনেই নিজেদের পড়ার খরচ তোলার জন্য টিউশান পড়াতেন। দাদা তো বেশি দূর পড়তেই পারলেন না৷ আই.এ পড়তে পড়তেই পোষ্ট অফিসে চাকরি পেয়ে গেলেন। সেইজন্য তিনি অবশ্য এম.এ অব্দি টানতে পেরেছেন।
দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে অরবিন্দ ঘরের বইপত্র, টুকরোটাকরা জিনিসপত্র সব পেটিতে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। রঙমিস্ত্রিরা নইলে জিনিসপত্র এমন টান মারবে, কোথাকার জিনিস কোথায় থাকবে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। এটা-ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত জিনিস সামনে এল। কত পুরোনো চিঠিপত্র, ওঁদের বিয়ের কার্ড, ছেলের অন্নপ্রাশনের কার্ড, ফটো আ্যালবাম -- আরও কত কী! আনমনে অরবিন্দ বিয়ের অ্যালবামটা খুললেন। নববধূর সাজে নীপা, শুভদৃষ্টি... চোখটা ঘোলাটে হয়ে গেল তাঁর। নীপা দাদারই শশুরবাড়ির তরফে এক আত্মীয়ের মেয়ে। এর আগে ওঁর জন্য অনেক সম্বন্ধ এসেছিল। অরবিন্দ সব নাকচ করে দিচ্ছিলেন। তখন ওঁর মা বেঁচে। কেন কে জানে, মনে মনে ওঁর ইচ্ছে ছিল উনি শহরের মেয়ে বিয়ে করবেন৷ দাদা একমাত্র এই কথাটা জানতেন। দাদাই তখন এই সম্বন্ধটা ঠিক করেছিলেন৷ নীপা অবশ্য পুরোপুরি শহরের মেয়ে নন। গ্রামেই ওঁদের বাড়ি, তবে ওঁর বাবা শহরে চাকরি করতেন বলে ওঁরা শহরেই মানুষ হয়েছেন। বাবার যদিও এই বিয়েতে খুব মত ছিল না। শহরের মেয়ে -- গ্রামে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, রান্নাবাড়ি পারবে কি না, এইসব সাধারণ যেসব উদ্বেগ গুরুজনদের হয় আর কী! দাদাই বুঝিয়েসুঝিয়ে বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন। এসব সম্পর্ক আজকালকার ছেলেছোকরারা কী বুঝবে। ছোটবেলায় দাদা ছিলেন গ্রামের সব সমবয়সি ছেলেদের কাছে হিরো। চমৎকার গড়ন। খেলাধুলোয়, দুষ্টুমিতে -- সব কিছুতেই সবার নেতা। সবাই চাইতো যে কোনও খেলায় তারা যেন দাদার দলেই থাকে। অরবিন্দ খেলাধুলোয় খুব পারদর্শী না হলেও দাদা নিজের দলে তাঁকে সব সময় রাখতেন। দাদার শরীর খারাপ হলে কী যে খারাপ লাগত তখন। একবার দাদার টাইফয়েড হয়েছিল। পাড়ার চণ্ডীতলায় তাঁর আরোগ্য কামনায় অরবিন্দ কত সিঁদুরের প্যাকেট যে মানত করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। পড়াশুনো বা কোনও কিছু নিয়ে বাবা তাঁকে কিছু বলতে এলেই দাদা গিয়ে সামনে দাঁড়াতেন। তা দাদা যখন আই.এ পড়ছিলেন, কীভাবে যেন বৌদির প্রেমে পড়ে গেলেন। বৌদি পাশের গ্রামেরই মেয়ে, অরবিন্দের সমবয়সী। দাদার অনেক চিঠি অরবিন্দও বয়ে নিয়ে গেছেন বৌদির কাছে। যখন বৌদি বি.এ পড়তে কলকাতায় এলেন, তখন দাদা চাকরি করছেন। অরবিন্দও তখন কলকাতার হস্টেলে। দাদা, ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসার নাম করে শনিবার হলেই কলকাতায় এসে ওঁর হস্টেলে উঠতেন। রবিবার সারাদিন বৌদির সাথে ঘুরেটুরে বিকেলবেলায় আবার বাড়ি ফিরে যেতেন। সত্যি, কী দিন ছিল সে সব! তখন কোথায় ছিলেন নীপা, কোথায় বা তপু, টুবাই, বাবাই। পাশে দেখলেন, নীপাও কখন এসে গোছানোতে হাত লাগিয়েছেন। অরবিন্দ বললেন, “বুঝলে নীপু, আগেকার দিনই ছিল ভালো। আমাদের মতো বয়েস হলে সবাই বানপ্রস্থে চলে যেত। কোনও কুট-কাচালি নেই।”
“সবাই যে যেত, কোথায় পেয়েছ?”
‘’কেন, তুমিও তো পড়েছ, ব্রহ্মচর্য, গার্হ্যস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।‘’
“ওটা তো থিওরিটিক্যাল ফাল্ডা। লোকে যেতো কি?’’
“যেত নিশ্চয়ই। নইলে বইতে লিখবে কেন?”
“একটা উদাহরণ দাও দেখি?”
“কেন, রামায়ণ, মহাভারত!”
“আচ্ছা, মহাভারতই ধরো। ওখানে কোনও বড় চরিত্রকে দেখেছ কি, যারা একটা নির্দিষ্ট বয়সে স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থে গেছে?”
“কেন, ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, মাদ্রী, এরা যায়নি ?”
“তাকে কি আর যাওয়া বলে? চারদিকে সব সর্বনাশ ঘটিয়ে, জীবনে সব রকমের কূট-কাচালির যষ্টীপুজো করে তবে গেল বানপ্রস্থে। তাতে নিজেরা অশান্তি ভোগ থেকে বাঁচল কি ?”
অরবিন্দ আর বেশি ঘাঁটালেন না। কথাটা তিনি নেহাত আবেগ থেকেই বলেছিলেন। রামায়ন, মহাভারতের গল্প সেই ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা। খুব স্পষ্ট মনে নেই এখন। বেশি ফাণ্ডা মারতে গেলে মুশকিল আছে৷ নীপা সদ্য সদ্য টিভিতে দেখেছেন, নিশ্চয়ই ধরে ফেলবেন।
২
বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন। এবার পুজোর সময় অরবিন্দ ভাবলেন একা গিয়েই নাহয় দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন। কলকাতার পুজো ফেলে তপু বা নীপাকে সরানো মুশকিল। বাবাও অনেকদিন ধরে ওঁকে আসার জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন, যা প্রায় ওঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। ষষ্ঠীর দিন ভোররাত থেকে উঠে তৈরি হতে শুরু করলেন তিনি৷ জামাকাপড় সব রাতেই গুছিয়ে রেখেছেন৷ স্নানটা শুধু সেরে নিলেন৷ নীপা চা-জলখাবার করে দিতে চাইলেন, তবে অরবিন্দ রাজি হলেন না। অর্ধেকের উপর পথ তো ট্রেনেই যাবেন৷ ওতে চা, ঝালমুড়ি নিয়ে অনেকে ওঠে। মিছিমিছি ভোর ভোর নীপার কষ্ট করার কী দরকার? তাঁকে জামাকাপড় পরতে দেখে নীপা বললেন, “যদি সুযোগ পাও কথাটা পেড়ো।”
“যাচ্ছি অসুস্থ বাবাকে দেখতে, এখন ওসব বলা যায়?” খিঁচিয়ে উঠলেন অরবিন্দ।
“আহা রাগ করছ কেন? আমি কি বলেছি আগ বাড়িয়ে তোমাকে কিছু বলতে? যদি কথা ওঠে, তবেই বোলো।'’
রাগ রাগ মুখ করে অরবিন্দ বেরিয়ে গেলেন৷ বাড়ি এসে দেখলেন, বাবার শরীরটা বেশ ভেঙে গেছে। প্রায় নব্বইয়ের মতো বয়েস, এতদিন দেখলে বোঝাই যেত না। এবার যেন বয়সটা চেহারায় থাবা মেরেছে। বাবা বরাবরই কর্মক্ষম ছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে জেল খেটেছেন। যখন ছেলেরা হলো, ওদের নাম রেখেছেন প্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে। একজনের নাম সূর্যসেন, অন্যের অরবিন্দ। ওঁরা চট্টোপাধ্যায় বলে দাদার নামটা বেশ অদ্ভুত দাঁড়াল, সূর্যসেন চট্টোপাধ্যায়। ছেলে, নাতিরা সব বাইরে বাইরে থাকে, এতে উনি কোনও আফসোস করেন না। তার মনে হয়, তাঁর শাখা-প্রশাখা যেখানেই গিয়ে শিকড় পাক সেখানেই যেন ছায়া দিতে পারে। রোজ সকালে নিয়ম করে এখনও চার মাইল হাঁটেন। এসে প্রাণায়াম সেরে পুজোপাঠ। দুপুরে একটু ভাতঘুম দিয়ে এটাওটা পড়েন। সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতেই শুয়ে পড়েন। খোলা বারান্দায় তাঁর বিছানা হয়। এখনও ফ্যান ব্যবহার করেন না। রাতে ঠান্ডা লাগলে, ঘরের ভেতর খাটেও বিছানা পাতা থাকে, সেখানে চলে যান। এবার সেই বাবার গলাতেও কেমন একটা বিষন্নতার সুর। সন্ধেবেলায় অরবিন্দের সাথে চা খেতে খেতে বললেন, আমাকে একটু নবদ্বীপে গুরুদেবের আশ্রমে দিন কয়েকের জন্য রেখে আসবি?’
“সে নাহয় দেব, কিন্তু ওখানে কেন যাবেন বাবা? গতবার ওখানে গিয়ে তো খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন আপনি।”
“তা এখানে থাকলে কি আর অসুখ হতো না? আজকাল আর ভালো লাগে না রে। বড় একঘেয়ে লাগে। এত বড় বাড়িঘর, তোরা কেউ থাকিস না, কে দেখবে? এই তো ক'দিন পর সুয্যি বড় বউমাকে নিয়ে বড় দাদুভাইয়ের বাড়ি যাবে। তখন কে সন্ধে দেবে, তুলসীমঞ্চেই বা কে প্রদীপ দেখাবে? ব্রাহ্মণের বাড়ি, শাঁখ না বাজালে চলে?”
“তা সে কদিন আপনি আমার কাছে চলুন না।”
“তাহলে এখানে পাহারা দেবে কে? আমি তো সব তোদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছি। তোরা যে যার মতো ব্যবস্থা কর। আমি আর যখের ধন আগলাতে পারব না৷”
অরবিন্দের মনে হলো, এই এক মওকা। এবারে কথাটা বলা যেতে পারে। বললেন, “বাবা, আপনি কথাটা তুললেন বলেই বলছি, আমি ভাবছি আমার পোরশানের এই বাস্তুজমিটা বিক্রি করে দেব৷ আমার একটু টাকাপয়সারও দরকার।”
হরিদেব একথা শুনে কিছুক্ষণ থম মেরে রইলেন। বললেন, “সুয্যিকে বলেছিস?”
“আজ্ঞে না৷ আপনার অনুমতি পেলে তবেই বলব।”
“দ্যাখ, আমি যখন জায়গাজমি তোদের নামে করে দিয়েছি, তা নিয়ে আর কোনও মতামত খাটাতে যাব না। তোর বিক্রি করার দরকার, যাকে খুশি বিক্রি কর। তবে ন্যায়ত আগে তোর দাদাকেই প্রস্তাবটা দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি৷”
“নিশ্চয়ই। আমি আজকেই দাদার সাথে কথা বলব।”
রাতে বেশ জমিয়েই খাওয়াদাওয়া হলো। বৌদির হাতের রান্নাও চমৎকার। আর বাড়ির শাক-সব্জি, তার স্বাদ কি আর বাজারের হাইব্রিড মালে পাওয়া যাবে? নানান গল্প-আড্ডায় যখন খাওয়া শেষ হলো, রাত তখন দশটা বাজে। কলকাতায় কিছু না, তবে গ্রামের হিসেবে অনেক। খাবার পর অরবিন্দ বললেন, “দাদা চল, একটু তুলসী দালানে বসি; একটা কথা ছিল৷”
“এত পরিশ্রম করে এসেছিস, আজ শুয়ে যা না হয়। কাল সকালে কথা বলব।”
“এত তাড়াতাড়ি কি আর শুই দাদা? শুলেও ঘুম আসবে না।“
“তাহলে চল, একটু বসি গিয়ে।”
একটা চাটাই পেতে ওঁরা দুজনে এসে বসলেন। সামান্য গৌরচন্দ্রিকা সেরে অরবিন্দ বললেন, “দাদা, আমার একটু টাকার দরকার। ভাবছি, আমার পোরশানের বাস্তুভিটেটা বেচে দেব।”
“সে কী রে? বাবা এখনও বেঁচে আছেন। এখন তুই বেচতে গেলে বাবার কিন্তু খারাপ লাগবে।”
“বাবাকে বলেছি। ওঁর অমত নেই।”
“তুই বাবাকেও বলেছিস? আগে তো আমাকে বলতে পারতিস। টাকা-পয়সার একটা ব্যবস্থ নিশ্চয়ই হয়ে যেতো। আর তোর এখন টাকারই বা কী এত প্রয়োজন হলো শুনি?”
“ওই তপুর পড়ার খরচ তো কম নয়। ভাবছি এবার এম.বি.এ-টাও করিয়ে দেব।”
“সে আর কত টাকা লাগবে? লাখ দেড়েক টাকা আমার আ্যাকাউন্টে আছে। আমি বরং তোকে কালকে দিয়ে দেব। তাছাড়া তপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট হতে তো আরও বছর খানেক লাগবে। আর দু'এক বছরের মধ্যে তো আমাদের গ্রামে রেল লাইন এসে যাবে। তখন দেখবি হু হু করে জায়গার দাম বাড়বে। তখন না হয় বিক্রির কথা ভাববি। এখন চেপে থাক।”
“আসলে পুবপাড়ার ঘোষেরা আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার তো এখন অনেক থোক টাকার দরকার। তাই ভাবছিলাম…”
“তাহলে বাস্তুভিটে কেন? তোর নামে যে জমি আছে, তার একখানা বেচে দে। ব্রাহ্মণের ভিটে, ঘোষেরা কিনছে শুনলে বাবা কষ্ট পাবেন। পুরোনো দিনের মানুষ তো!”
“আসলে ওরা বাস্তুটাতেই ইন্টারেষ্ট দেখাচ্ছে। এখন ওদের পরিবার তো অনেক বড় হয়ে গেছে। যতটুকু ওদের বাস্তুভিটে, ততটায় ওদের সংকুলান হচ্ছে না। একসাথে সবাই মিলে থাকলেও অশান্তি। তাই ওরা আমাকে খুব ধরেছে। আমি ওদের বলেছি, এই জমিতে আগে দাদার অধিকার। দাদা যদি এটা নিতে রাজি না হয়, তবেই ওদের সাথে কথা বলব।”
“তা কত করে দাম দিতে চায় তারা?”
“কাঠা প্রতি চল্লিশ হাজার। ধরো আমার ভাগে দু'বিঘে আছে, মানে ষোলো লক্ষ টাকা।”
“সে তো অনেক টাকা রে! অত টাকা আমি পাবো কোথায়? তোর তো টাকাই দরকার, না হলে এর বদলে একটা জমি না হয় তোকে দিয়ে দিতাম।”
“টুবাই তো এখন ভালো টাকা মাইনে পায়। ও রাজি হবে না?”
“ক’দিন আগেই ও কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে৷ নাতি হলো ক’দিন আগে। বুঝতেই পারছিস, তার পেছনেও বড় খরচ। সব থেকে বড় কথা, এখনকার ছেলেছোকরা, গ্রামে জায়গা কিনতে ইন্টারেষ্ট দেখাবে বলে মনে হয় তোর?”
“তাহলে কী করব? ঘোষেদের সাথে কথা বলবো?”
“আমাকে কয়েকদিন ভাবতে দে। তোকে ফোন করে জানিয়ে দেব।”
সব শুনে নীপা টিপ্পনি কাটলেন, “ক’দিন ভাবতে দে মানে বড়গিন্নির বুদ্ধি নেওয়ার সময় দে। এমন একটা সম্ভাবনা তো কমন পড়েনি, নাহলে পরামর্শটা আগেই সেরে রাখতেন।”
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন অরবিন্দ। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, “মুখ সামলে কথা বলো নীপা। আমি বাড়ি এসে এসেই তোমাদের সবিস্তারে ব্যাখ্যান দিতে বসেছি আর তোমাদের বুদ্ধি নিচ্ছি, এতে দোষ হয় না; শুধু দাদা বৌদির সাথে এতবড় বিষয় নিয়ে পরামর্শ করলে দোষ?”
“দোষ কেন হবে? নারী-বুদ্ধি ছাড়া কি সংসার চলে?”
“হ্যাঁ, সর্বনাশা বুদ্ধি আর কে দেবে বলো?”
“আমার বুদ্ধি না নিয়ে তুমি চলতে পারতে? শিয়াল-শকুনে ছিঁড়ে খেতো। না না, শিয়াল-শকুন তো অনেক বড় কথা, মশা-পিঁপড়েও তোমায় কামড়ে খেতো।”
“কী ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া লাগিয়েছ তোমরা?” বেশ বিজ্ঞের মতো বলে উঠল তপু। “একদিক থেকে ভালোই হয়েছে বাবা। জেঠুরা এটা কিনতে না চাইলেই ভালো। রেল লাইন আসছে, এই মওকায় তুমি দর কষাকষি করে টাকাটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারবে। জেঠুরা কিনলে তোমাকে ষোলোর কমেই ছাড়তে হবে। ওদের যা হাত কচলানো স্বভাব!”
“কিন্তু ব্রাহ্মণের ভিটেতে ঘোষদের ঢোকালে বাবা মনে হয় সত্যিই কষ্ট পাবেন।' বেশ আন্তরিক শোনাল নীপা’র গলা।
“ছাড়ো তো মা। এসব সিম্পলি জেঠুদের বাগড়া দেওয়ার তাল। আমরা কি ওখানে থাকতে যাচ্ছি? কায়েত-কৈবর্ত্য যে ঢুকুক, আমাদের দেখার দরকার নেই।“
হে ঈশ্বর, কী বিষয়বুদ্ধি এখনকার ছেলেমেয়েদের! ক্রমশ কানমাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল তাঁর৷। চোখেমুখে একটু জল দেওয়া দরকার। অসহায় আক্রোশে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নিস্ফল পৌরুষে বাথরুমের দরজা কেবল সশব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “দড়াম”।

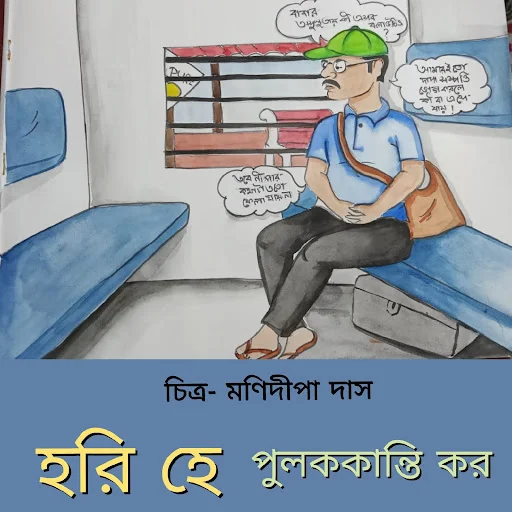














0 Comments