হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড ও বিদ্যাসাগর
প্রসূন কাঞ্জিলাল
অতীতের বাঙালীর হিন্দু-পরিবারগুলি সাধারণতঃ একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর ছিল। কোনো কারণে সেই উপার্জনক্ষম পুরুষের মৃত্যু ঘটলে পরিবারের স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহায় অনাথের মতো বিপন্ন বোধ করতেন। তাই সেই পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিদ্যাসাগর ‘অ্যানুইটি ফান্ড’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন ছাড়াও বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম বড় ও মহৎ কীর্তি ছিল এই ‘হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড’। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বর্তমানে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কোন লেখায়, তাঁর জীবনের সেই অন্যতম মহৎ কীর্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতীতের বিদ্যাসাগর গবেষকদের লেখা থেকেও এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।
বিষয়টাকে বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সাথে বা পেনশন প্ল্যানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে বিদ্যাসাগর যে ওই সময়ে এই ধরণের কোন সঞ্চয় প্রকল্পের কথা ভাবতে পেরেছিলেন, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, যিনি মাসে মাসে ওই ফান্ডে কিছু টাকা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পরে স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশি যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন। যেমন, যদি কেউ মনে করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসিক ৫ টাকা করে সাহায্য পাবেন, তাহলে তাঁকে প্রতিমাসে আন্দাজ ২ টাকা করে ওই ফান্ডে জমা দিয়ে যেতে হত। এইভাবে অ্যানুইটি ফান্ডে মাসিক ৩০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
১৮৭২ সালের ১৫ই জুন তারিখে উক্ত ফান্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার আগে, ১৮৭২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে’ একটি সভা করে ওই ফান্ডটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। প্রথমে ১০ জন ‘সাবস্ক্রাইবার’ নিয়ে ‘৩২নং কলেজ স্ট্রিটে’ উক্ত ফান্ডের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজারা সেই জনহিতকর কাজে প্রথম এগিয়ে এসে ফান্ডে একত্রে ২,৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ফান্ডের প্রথম দু’বছরের ট্রাস্টি ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র । তৃতীয় বছর দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হওয়ার পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর মিলিত ভাবে ওই ফান্ডের ট্রাস্টি হয়েছিলেন। ফান্ডটি প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে। ডেপুটি-চেয়ারম্যান ছিলেন মুরলীধর সেন, এবং ডিরেক্টরবোর্ডের সভ্যরা ছিলেন - সেকালের প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাবস্ক্রাইবারদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ছিলেন।
🍂১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বছর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ওই অ্যানুইটি ফান্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ফান্ডের ডিরেক্টরদের কাছে একটি পত্র লিখে উক্ত ফান্ডের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
এরপরে ১৮৭৬ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে ‘হিন্দু স্কুলের’ একটি সভায় ফান্ডের ডিরেক্টররা তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চেয়েছিলেন।
২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিদ্যাসাগর ফুলস্কেপ কাগজের প্রায় কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পত্র তাঁদের সেই ‘কারণ’ সম্পর্কে অবগত করেছিলেন। সাধারণভাবে যে-কারণে আজও বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিদ্যাসাগর ঠিক সেই কারণগুলিই তাঁর পত্রে বিবৃত করেছিলেন। তাঁর মূল অভিযোগ ছিল যে, ফান্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক নেই, নিয়মকানুনের বালাই নেই, এবং সভার রিপোর্ট ঠিক রাখা হয় না। এছাড়া ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না করে নিজেদের কর্তৃত্ব ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন। এই ধরনের বহু অভিযোগ করে ওই পত্রের শেষের দিকে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন -
“এই ফন্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাঁহার পরম ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফন্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফন্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এবিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত 'নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।
বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; তথাপি আপনারা আমার উপর এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফন্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফন্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি, জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে-বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।'
ভবদীয়স্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কলিকাতা
১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল।”
এরপরে ডিরেক্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগরের মত বদলাতে পারেননি। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডের সঙ্গে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্র মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর পদাঙ্ক অনুসররণ করেছিলেন। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ডের পক্ষে সেই আঘাত কাটিয়ে ওঠা বেশ কঠিন হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনায় তাদের উপকারই হয়েছিল। নিজেদের দোষত্রুটির সমালোচনা ও সংশোধন করে, পরবর্তীকালে তাঁরা আত্মোন্নতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দোষ যে শুধু তাঁদেরই একারই ছিল তা নয়, বিদ্যাসাগরেরও ছিল। ইতিহাস বলে যে, বিদ্যাসাগরচরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল তাঁর নিরাপস মনোভাব। কারো সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে তিনি খুব একটা কাজকর্ম করতে পারেন নি। তাঁর সততা নিষ্ঠা বিশ্বাস অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে কেউ সায় দিয়ে চলতে না পারলে, তিনি তাঁর সঙ্গে এক-পাও চলতে পারতেন না। সেজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বহুলোকের সম্মিলিত কাজকর্মে তিনি খুব বেশিদিন সহযোগিতা করতে পারেননি। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডের ক্ষেত্রেও কিছুটা সেটাই ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং সেই ফান্ড তাঁর কর্মজীবনের একটা বড় কীর্তি ছিল ।।
তথ্যসূত্র --
১- বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার।
২- বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ।
৩- বিদ্যাসাগর, চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়।
৪- বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
৫- বিদ্যাসাগর - জীবনচরিত ও ভ্ৰমনিরাশ, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৬। বিহারীলাল সরকার , বিদ্যাসাগর, ১৮৯৫,

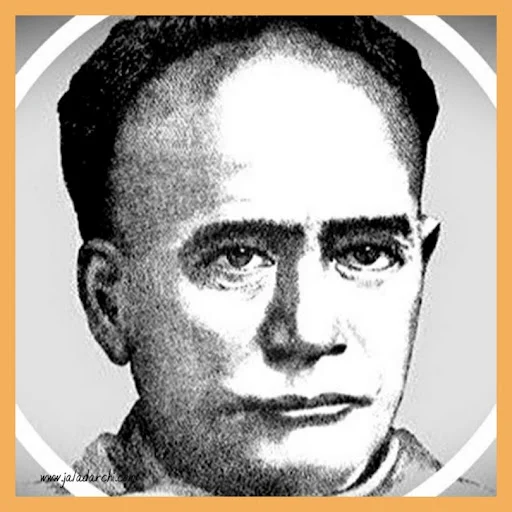














0 Comments