স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কের রসায়ন
প্রসূণ কাঞ্জিলাল
সেদিন ১৮৮৩ সালের ৭ই এপ্রিল, শ্রী রামকৃষ্ণএর চরণ তলে বসে রবীন্দ্র সংগীত গাইছেন নরেন্দ্র নাথ, এমন এক অমোঘ মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিল এ বিশ্ব প্রকৃতি, যেনো তিন ভুবন মিশেছিল কোনো দৈব ঈশারায়।
নরেন্দ্র নাথ গেয়েছিলেন
"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি–
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।।"
১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন। তারপর থেকেই তাঁর সান্নিধ্যে আসা ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রবল উন্মেষ। পরমহংসদেবকে তিনি প্রায়ই গান গেয়ে শোনাতেন। পরমহংসদেবও নরেন্দ্রর সুকণ্ঠের সংগীতে এক-একদিন মুগ্ধ হয়ে ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হয়ে যেতেন এমন তথ্য পাওয়া যায়। তাঁকে শোনানো গানগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-রচিত কয়েকটি গানও আছে।
রবীন্দ্র-রচিত যে গানগুলি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন সেগুলির কালানুক্রমিক তালিকা (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অনুযায়ী) হল :--
১. গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে (২৫ চৈত্র ১২৮৯, শনিবার, ৭ এপ্রিল ১৮৮৩)।
২. দিবানিশি করিয়া যতন (৩০ ভাদ্র ১২৯১, রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪)।
৩. দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে (২৯ ফাল্গুন ১২৯১, বুধবার, ১১ মার্চ ১৮৮৫) উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে পাঠ আছে ‘সব
দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে’, তাই অনেকের ধারণা হতে পারে এটি রবীন্দ্রসংগীত নয়। কিন্তু এটি অবশ্যই রবীন্দ্র রচিত এবং ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত গানেরই পাঠান্তর।
৪. তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (৩১ আষাঢ় ১২৯২, মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ১৮৮৫)।
৫. মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ (৯ কার্তিক ১২৯২, শনিবার, ২৪ অক্টোবর ১৮৮৫)।
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার প্রমথনাথ বসু জানিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ বি.এ পরীক্ষার প্রথম দিন (৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩,সোমবার,
১৭ পৌষ ১২৯০) প্রত্যূষে চোরাবাগানে বন্ধু হরিদাস ও দাশরথির বাসার সামনে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ ১৩২৬, পৃ. ৯০-৯১)।
৬. এ কী সুন্দর শোভা (১২ কার্তিক ১২৯২, মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫)।
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন: “আমার ভাগ্য এমন যে, প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই কাশীতে। আর যাঁর কণ্ঠে সেই গানটি ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর নাম শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। গানটি কাশীতে গেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক স্থানে আমি এই কথাটি সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছি।
সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি অতিপ্রিয় গান একখানি বইয়ে মুদ্রিত আকারে পেয়েছি। গানটি :
এ কী এ সুন্দরশোভা! কী মুখ হেরি এ। আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম-উৎস উথলিল আজি
বলো হে প্রেমময়,
হৃদয়ের স্বামী
কী ধন তোমারে দিব উপহার।
স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব গাইয়ে ছিলেন।কাশীতে আর দুটি গান বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। সব কটি গানই রবীন্দ্রনাথের—
-
মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না-
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি৷৷
সখী, আমার দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারী।
কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।”
সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রনাথ যে তাঁর বন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে ‘সঙ্গীত কল্পতরু' (ভাদ্র ১২৯৪) নামে একটি সংগীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, সে-কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গৃহীত হয়। প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর ‘বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন : “সন্ন্যাস গ্রহণের আগে... একটি সঙ্গীত-সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্কলন কার্যে তাঁর অনেকটা হাতে ছিল। ... বইটির নাম 'সঙ্গীত কল্পতরু'।
'শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি.এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।'...
‘পাঠক-সমাজে এই সঙ্গীত-সঙ্কলনটি কি অসাধারণ জনপ্রিযতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের মাঘ মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১২৯৫-এর জ্যৈষ্ঠে তৃতীয় সংস্করণ।
“... সেকালের জনপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি বিবাদিনী বীণা', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ... এ সঙ্কলনে সংগৃহীত।
🍂
আরও পড়ুন 👇
“...রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি’ এবং 'কালী কালী বলো রে আজ' গান দুইটির নির্বাচন লক্ষণীয়।”
এ ছাড়াও ‘ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি' এবং 'তুমি কি গো পিতা আমাদের'— এ দুটি রবীন্দ্রসংগীতও ওই ‘সঙ্গীত কল্পতরু গ্রন্থে স্থান পায়।
' সঙ্গীত কল্পতরু ' গ্রন্থের ভূমিকায় ' সঙ্গীত ও বাদ্য ' প্রবন্ধে স্বরসাধনা' অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটির প্রথম দুটি ছত্র ভৈরব রাগের সরগম নিয়ে ভৈরব কাওয়ালিতে স্বরলিপি দিয়েছেন বিবেকানন্দ।এ ৺তার সুর সংযোজনায় কৃতিত্বের পরিচায়ক।
এসব তথ্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র সংগীত ও সুরের মূর্ছনার পথকে আশ্রয় করে
আধ্যাত্মবাদী মনন সৃষ্টির এক অনন্য পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। অতন্ত্য সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন স্বামীজি। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ৺তার প্রিয় শিষ্যর গান শুনতে খুবই
ভালোবাসতেন।
স্বামীজি ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সরাসরি বাক্যালাপ এর তথ্য না থাকলেও ,একজনের সৃষ্টির প্রতি অপরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে এখনও এটা বিস্ময়কর যে, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ - সমকালে দুই বিশ্ববিখ্যাত মনীষী পরস্পরের সম্পর্কে আপেক্ষিক নীরবতা অবলম্বন করে গেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?
স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তেমন কোনও কথা বলেছেন বলে জানা না গেলেও, রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে-সেখানে অনেক কথা বলেছেন তা অজানা নয়। অবশ্য তাকে নিয়ে কোনও স্বতন্ত্র রচনা যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে নেই সে-কথা ঠিক।তবে উভয় উভয়কে যে প্রত্যক্ষ চিনতেন এবং তাঁদের মধ্যে যে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল তার প্রমাণও তো যথেষ্টই আছে।
বিশ্বধর্মসম্মেলন শেষ হলেও স্বামীজীর ভাবধারা - মূলতঃ বেদান্তভিত্তিক প্রচার করার জন্য সংবাদপত্রে তাঁর গুণগান ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি পাশ্চাত্যেই থেকে গেলেন আরও প্রায় তিন বছর। ঘুরলেন ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যত্র। পাশ্চাত্যের ১৮৯৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশজননীর কোলে ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন। ১৮৯৭-এর ১৫ই জানুয়ারী কলম্বোয় এসে
পৌঁছান। এরপর স্বদেশবাসীর কাছ থেকে অভিনন্দনের ঢেউ এসে আনন্দসাগরবারিতে অভিস্নাত করে দিল তাঁকে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা পৌঁছালেন। দেশের সংবাদগুলিতেও অন্যতম প্রধান সংবাদ হয়ে উঠল স্বামীজীর এই বিশ্বজয়। ভারতবাসীর হীনমন্যতা কাটতে শুরু করল। চমকপ্রদ আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল দেশবাসীর মনে- তাহলে ভারতবর্ষেরও এমনকিছু আছে, যা জগতের কাছে মর্যাদা পেতে পারে। ফেরার সময় তিনি দেশ সেবার জন্য নিয়ে আসতে পেরেছেন বেশ কিছু অর্থ আর নানা দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান। তার ভিত্তিতে দেশকে বোঝালেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও একান্তই প্রয়োজন। এটা ধর্মেরই অঙ্গ। গুরুর ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবা’ - র আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু হল তাঁর এই মহান যাত্রা।
একটা প্রশ্নই এসে পড়ে, বিবেকানন্দেরই প্রায় সমবয়সী আর একজন ভারত সস্তান যাঁর জন্য বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী বিশ্বের আঙ্গিনায় গৌরব লাভ করেছে, সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, আর বিবেকানন্দেরই বা মনোভাব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে সময় কেমন ছিল? সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, উভয়ের সম্পর্ক কাছের ছিল না, একটা শীতলতা ছিল দু'জনের মাঝখানে। অনেকেই আবার এসব নিয়ে গল্পকাহিনী লিখে বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বহুকাল ধরে। এবার কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা দেখি কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারি।
রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১, নরেন্দ্রনাথের ১৮৬৩।রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, আর নরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকে প্রায়শই ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। দেবেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হিসাবেও নরেন্দ্রনাথকে আমরা পাই। তাছাড়া বৈষ্ণচরণ বসাকের সঙ্গে যৌথভাবে নরেন্দ্রনাথ ‘সঙ্গীত কল্পতরু' শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ৮টি গান সঙ্কলিত করেছেন। নানা পরিস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ২৫টির বেশী গান পরিবেশন করেছিলেন বলেও তথ্য পাওয়া গেছে। তবে যখন স্বামীজী ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে তারপর বিশ্বজয়ে বেরোলেন, তখন অগণিত মানুষের দুঃখ, প্রত্যাশা, আনন্দ, আস্থাকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করে বিশ্বকে প্রেমের ঐক্যে বাঁধতে ও সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তখন রবীন্দ্রনাথের মনোজগৎ মূলতঃ ব্যক্তিজীবনের প্রেম-বিরহ, প্রকৃতি-মুগ্ধতা ও ব্রাহ্মসমাজের সীমানায় সাধনার মধ্যেই মগ্ন ছিল। তাই তখন সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব আসা স্বাভাবিক। কারণ তখনও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার, বিশ্বহিতের যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেওয়ার সংকল্প স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি। কিন্তু বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর নাগরিকদের পক্ষ থেকে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে এক বৃহৎ সভায় তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে যে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন – তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ -এর ৩রা মার্চ ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায়।
স্বামী বিবেকানন্দ যখন ১৮৯৭ সালে বেদান্ত বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন সেই সভায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা শ্রবণের প্রতিক্রিয়া রূপে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'উপনিষদ ও স্বামী বিবেকানন্দ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩০৩ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'স্বাগত অভিবাদন ' জানিয়ে লেখেন "তাহার যেরূপ প্রশান্ত সৌমমূর্তি, ভব্য বৈরাগ্য পরিচ্ছদ, তাহার যে রূপ বাক পটুতা, শাস্ত্র পারদর্শিতা ও উৎসাহ উদ্যম তাহাতে তিনি যে তাহার উদ্দেশ্য সাধনে সফল মনোরথ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।"
১৫ মাঘ ১৩০৫ (শনিবার ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯) রবীন্দ্র-বিবেকানন্দের দুর্লভ প্রত্যক্ষ মিলনে অভিসিঞ্চিত এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এদিন সকালে ছিল জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে ব্রাহ্ম সম্মেলন। সন্ধ্যায় ছিল নিবেদিতা আয়োজিত এক চা-পানের আসর। এই চা-পানের আসরে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। অবশ্য ধারণা করা যায় ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ হওয়ার আগে সংগীতকুশলী নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়ে থাকবে ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবে বা অন্য কোনও সংগীত সভায় তবে সে কেবল অনুমান ভিত্তিক যেহেতু তেমন কোনও নির্দিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষিত
থাকেনি।
নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেম [Lizelle Raymond) জানিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও এঁদের বন্ধুত্ব হল। তিনি তখন শিলাইদহ থেকে একরাশ কবিতা লিখে ফিরে এসেছেন, সে-সব কবিতা বাংলার গর্বের ধন।' (অনুবাদ—নারায়ণী দেবী, নিবেদিতা (১৩৬২), পৃ. ২৫৮)। মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার সৌজন্যে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে তাঁকে তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন ছাড়াও ডাঃ পি. কে. রায় ও তাঁর পত্নী, জগদীশচন্দ্র বসু ও আরও বিশিষ্ট কেউ কেউ। এ-সময় বিবেকানন্দ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এই যোগাযোগকে সমর্থন করে নিবেদিতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—
'Make inroads to the Brahmos' অর্থাৎ 'ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়ো।'
চা-চক্র শেষ হওয়ার পর তার বিবরণ দিয়ে ৩১জানুয়ারি ১৮৯৯ (১৮ মাঘ ১৩০৫) নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন : ------
"On Saturday also I had a sort of unarranged party.
Mrs. P. K. Roy and young Mr. Mukherji [?], Mr. Mohini and the poet-and presently Swami with Dr. Sirkar [Mahanderalal]. It was a brilliant little gathering, for Mr. Tagore sang 3 of his own compositions in a lovely tenor- and Swami was lovely. Only there was some cloud I could not tell what..... At this moment the evensong gongs and bells are sounding in the homes all around me. It is the hour that they call 'candle light'- the hour of worship. I cannot forget the lovely poem 'come O peace' (Esoho Shanti) with its plaintive minor air, that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time." [Letters of Sister Nivedita (1982), Vol. I, pp. 43-45]
এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় –
নিবেদিতার বর্ণনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মধ্যে কথোপকথনের কোনও উল্লেখ নেই। সামান্য হলেও সৌজন্যের খাতিরে দু'একটি কথা হয়ে থাকতে পারে এমন অনুমানে বাধা কোথায়? তবে 'Only there was some cloud - I could not tell what' উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বড়ই ইঙ্গিতবহ। তবে ১২ই মার্চ, ১৮৯৯ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রে লিখবেন
কেন – “He (Vivekananda) said as long as you go on mixing with that [Tagore] family Margot I must go on sounding this gong. Remember that family has poured a flood of erotic venom over Bengal.' Then he described some of their poetry." [Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 82]
ধারণা করা যায়, এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথে পূর্বরচিত 'কড়ি ও কোমল’-এর দেহাশ্রয়ী
রোমান্সরসে ভরপুর কবিতাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করে থাকবেন। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের ‘পরিব্রাজক' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ
‘নৈবেদ্য' রচনার যুগে পৌঁছে গেছেন, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আধ্যাত্মিকতাবোধ কবির মানসলোককে আচ্ছন্ন করেছে। তাই নিবেদিতার প্রতি এ ধরনের নির্দেশবাক্য দেখে মনে হয়।
বিবেকানন্দ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা যে বিবেকানন্দের এ-ধরনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন তা নয়। তিনি রবীন্দ্র-সান্নিধ্য পেতে যে আগ্রহী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর কিছু পত্রে।
রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্ক নির্ণয়ে এই সব তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে রবীন্দ্রসান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেও, ব্রাহ্মসমাজের তথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অসদ্ভাব ছিল তা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। তার দৃষ্টান্ত-৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (মঙ্গলবার ১৬ মে ১৮৯৯) মহর্ষির তিরাশিতম জন্মোৎসবে নিবেদিতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আগমন। পরদিন ১৭ মে বুধবার (১৮৯৯) তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন: “Yesterday was Devendranath Tagore's birthday. I took a branch of the Dukhineswar Bo Tree with Swami's pranams [Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 145. L.No. 43]
বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় নীরব ও উদাসীন থেকেই গিয়েছেন একথা যেমন ঠিক, তেমনই রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি ৺তার যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তারও বহু প্রমাণাদি পাওয়া যায় । রবীন্দ্র সংগীত প্রীতির সঙ্গে এও উল্লেখ্য যে বিবেকানন্দ, জাপানের বিখ্যাত কবি ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটি খুব গুরুত্বপুর্ণ। ভারতবর্ষকে বুঝতে ওকাকুরা বিবেকানন্দের কাছে গেলে তিনি বলেছিলেন- “এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন”। এই কথা বিবেকানন্দের রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মকে সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রবীন্দ্ররচনায় বিবেকানন্দের নামোল্লেখ প্রথম লক্ষ্য করা যায় ‘সমাজভেদ প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ‘স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত। বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। ১৯০১-এর জানুয়ারি Contemporary Review পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ ডিলন লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ রচিত। যেখানে চিনাদের উপর য়ুরোপীয়দের অকথ্য অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের নামোল্লেখ করে বলেন :--
‘বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রাতন্ত্র। (রবীন্দ্ররচনাবলী-৬, সুলভ সং, পৃ. ৫০৯)। বলা বাহুল্য, এর এক বছর পরেই বিবেকানন্দ প্রয়াত হন।বিবেকানন্দের দেহাবসান ঘটে ২০ আষাঢ় ১৩০৯ (শুক্রবার ৪ জুলাই ১৯০২) রাত্রি ৯ টায়। মান উনচল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে মাত্র দশ বছরের কর্মতৎপরতায় তিনি জাতির জীবনে যে গভীর প্রভাব রেখে যান তা আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাঁর এই অকাল প্রয়াণ রবীন্দ্ররচনায় কোনও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও মাত্র কয়েকদিন পরে ২৮ আষাঢ় ১৩০৯ (শনিবার ১২ জুলাই ১৯০২) ভবানীপুরে সাউথ সাবারবার্ন স্কুলে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভপতির ভাষণে তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।
দুঃখের বিষয়, এই শোকসভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে উক্তিগুলি করেছিলেন তার অনুলিখন সংগৃহীত হয়নি।
বিবেকানন্দের অন্তর্ধানের পরে ১৯০৪ সালে ১৩ অক্টোবর, গয়ায় বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকালে নিবেদিতা স্বামীজি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সেই সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এর কয়েক বছর পরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট ১৯০৮) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে অনুষ্ঠিত আর একটি ছাত্রসভাতেও রবীন্দ্রনাথ এই অকাল প্রয়াত মনীষীকে স্মরণ করে বলেছিলেন: অল্পদিন পূর্বে বাঙলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে
পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' ('পূর্ব ওপশ্চিম’: সমাজ, রবীন্দ্ররচনাবলী-৬, সুলভ সং, পৃ. ৫৫২)।
১৯২৮ সালের ৪ এপ্রিল ডা: সরলীলাল সরকারের এক পত্রের উত্তরে অমিয় চক্রবর্তী কবির পক্ষে যে পত্র দেন, তার অনুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং নিম্নোক্ত অংশটি লেখেন, যেখানে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।
' ......... বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে-সব. দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়। ভয় হয় ,পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোঘোধিত তেজকে চাপা দিয়ে স্নান করে দেয় – কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।' (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৭ম খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ৫৩৩-৩৪)। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির 'চরকা কাটো' আন্দোলনকে বর্জন করে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।
১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে রবীন্দ্রনাথ স্বামী অশোকানন্দকে লেখা এক পত্রে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছিলেন:
‘কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ সেবা পেতে
চান। একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোনো বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে—তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে, মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।' (দ্রষ্টব্য : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭১ মাঘ-চৈত্র/বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৪)। দিলীপ কুমার রায় তার 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা ' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি উদ্ধার করেছেন।
১৯২০ সালে
জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা নিয়লন্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কে কবিগুরু স্বামীজি সম্পর্কে বলেছেন ' ........ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’ বলে— কাঁদুনি গান নি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকে তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য কীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি–আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন : ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও – তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড়ো করে দেখো না। আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন ‘দুটি ভিক্ষে পাই গো বলে, তা হলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।” (দ্রষ্টব্য : বিশ্ববিবেক, পৃ. ২১০-১১)।
কবিগুরুর বিখ্যাত এক উক্তি ,আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে ,সেটি হলো - রবীন্দ্রনাথ রোমারোলাঁকে বলেছিলেন, ‘যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক,
নেতিবাচক কিছুই নেই।'
রম্যা বলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯ এপ্রিল ১৯২১ (মঙ্গলবার ৬ বৈশাখ ১৩২৮) প্যারিসে। এই দুই মনীষীর প্রথম সাক্ষাৎকার বিশ্বভারতীর আদর্শ, শান্তিবাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সমস্যা, গান্ধীজির উপর তলস্তয়ের প্রভাব এবং বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য হয়। এই সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃত হল
Tagore : I have never been able to love the God of the Old Testament. He is the Lord with the rod. Rolland But even in the New Testament the same motive occurs. Jesus is the Lamb and the Lord sacrificed
for the sake of humanity. The emphasis is wrongly placed and the attitude is not spiritual in the large sense. Do you think that Vivekananda in India tried to check the abuses
in this line? Tagore: So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life....We must rise
higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could toleratemany religious habits and customs which have nothing spritual about them. My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil, it is like, sunlight which makes the existence of evil germs impossible. As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may be good to India to-day, for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith. It will sweep away all obnoxious undergrowths and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West, will be of value to a large section of Indian people.'
[Vide Rolland and Tagore, ed. Alex Armson &
Krishna Kripalani (1945), p. 100]
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের কেবল পৌরুষ ও আত্মমর্যাদার প্রশংসা করেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর রচনায় চলিত ভাষারীতিরও বিশেষ
প্রশংসা করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে কুমুদবন্ধু সেন ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় (মাঘ ১৩৪৪) লিখেছেন :
“আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে—তাহার প্রেরণা যোগাইয়াছে স্বামীজীর বাংলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার
‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা’ ও ‘পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে।রবীন্দ্রনাথই প্রথম বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত চলিত গদ্যরীতির প্রধান সমর্থক হয়ে সপ্রশংস সমালোচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রে স্বামীজির ছায়া পরিলক্ষিত হয়।
রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় খুব অসঙ্কোচে মন্তব্য করেছেন : “গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না।” (রবীন্দ্রজীবনী-২, পৃ. ২৩৫)। আমাদেরও ধারণা গোরা চরিত্রে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা এই দ্বৈত সত্তার মিশ্র প্রতিফলনকে কেউ অবিশ্বাস করবেন না। কেন না,রবীন্দ্রনাথেরই নানা ছোটখাট উক্তি ও মন্তব্যে ছড়িয়ে আছে এই মতের সমর্থন।
সমকালের দুই অসামান্য নর-নারী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের মননে কতখানি ছায়া ফেলেছিলেন তার আরও দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে।
রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একে অপরের জীবদ্দশায় আদৌ মুখ খোলেননি, অথচ স্বদেশ ভাবনায় বা মানব ভাবনায় দু'জনেই মিল ও
অমিল নিয়ে বড় বেশি তুলনীয় হয়ে ওঠেন। কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং “বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ”-এর ইতিহাস ব্যাখ্যাতা শঙ্করীপ্রসাদ বসু দু'জনেই এই দুই সমকালীন ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু মৌল সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন।একই কলকাতা শহরের বুকে মাত্র স্বল্প দূরত্বে দু'জনের জন্ম ও জীবন পরিক্রমা শুরু। বয়সের ব্যবধান মাত্র দেড় বছরের। উভয়ের মধ্যে চিন্তাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ দেশ ও জাতির মধ্যে জীবনের গতিবেগ ও জীবনানুরাগ, সংগ্রামী চেতনা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে চাইছেন। আর তাঁর প্রয়াণের পরেই স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ থেকে শুরু করে সারা জীবন ধরে জাতির মর্মমূলে আত্মবিশ্বাসও আত্মনির্ভরতা জাগ্রত করবার মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আধ্যাত্মিকতা উভয়ের জীবনের কেন্দ্রস্থলে ছিল। তাই রবীন্দ্র-বিবেকানন্দের এই চিন্তাগত সাদৃশ্য আজ যথেষ্ট গবেষণার বিষয়।
স্বামীজির অকাল প্রয়াণ বাংলা তথা সারা ভারতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। স্বামীজির দর্শন, আধ্যাত্মবাদ, দেশপ্রেম আপামর ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করেছিল। আর বিশ্বকবির অবদান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন,জাতিগঠন, মনন , চিন্তনের রসদ হয়ে থাকবে চিরকাল।বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সমন্ধে বিস্তারিত কোনো রচনা বা বক্তব্য না রাখলেও উনি ইহলোকে থাকাকালীন কবির সৃষ্টি ও সৃজনের অনুরাগী ছিলেন, একথা প্রমাণিত।
পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ভূমিকা, শান্তিনিকেতন গঠন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি - এসবের খবর পাওয়ার সুযোগ পেয়ে তবে যদি এই পৃথিবী ছেড়ে প্রস্থান করতেন স্বামী বিবেকানন্দ তাহলে অবশ্যই যে অভিনন্দিত করতেন শৈশবের বন্ধুকে, তা বলাই বাহুল্য।
সেই পরমলগ্নের মহান প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল বাংলা তথা ভারত তথা পৃথিবী।।
তথ্যসূত্র :
১)‘সবার স্বামীজী’ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার,
২) বিবেকানন্দ - ‘জীবন ও বাণী’ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বেলুর মঠ,
৩) কলকাতা পুরশ্রী জানুয়ারি ২০১৩ ( স্বামী বিবেকানন্দ - সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংকলন)
৪) ‘উদ্বোধন’, স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংখ্যা।



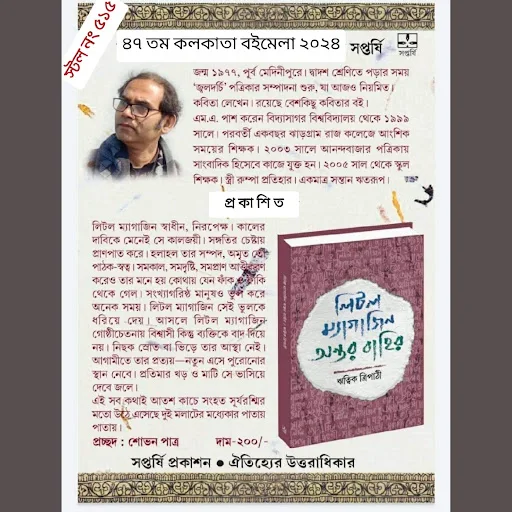












1 Comments
ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ
ReplyDelete