চিত্রা ভট্টাচার্য্য
স্বদেশ প্রেমিক কবি , স্বাধীনচেতা শৃঙ্খল জর্জরিত জীবন তাঁর কোনোদিনই কাম্য ছিলনা । স্বাধীনতার কঠিন সাধনায় ব্রতী তিনি ভাবেন যিনি নিজে স্বাধীন নন, তার পক্ষে অন্যকে কিংবা জাতিকে স্বাধীন করা কোনো মতে সম্ভব নয়। উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন সাম্যের গান। মুক্তির প্রেরণা হয়ে চিরদিন বিরাজ করছেন বাঙালির মননে । তাঁর বিশ্বাস ছিল মুক্তির জন্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় ভারতবাসীকে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে কবি আগেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।
এরপর মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত কবির ' কামাল পাশা '' নিয়ে লেখা মর্মস্পর্শী রোমহর্ষক একটি অনুচ্ছেদ এই আলোচনায় প্রথমেই মনেপড়ে ---
''তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আশমানের আঙিনা তখন কারবালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রিক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা মহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহাকল্লোলে অম্বর ধরণি কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুইজন করিয়া নিহত সৈনিক বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলাগুলির আঘাতে, বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্ত-রঞ্জিত। তাহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ও নাই। উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন খেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙা সঙিনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া, ভাঙা খাটিয়া আদি দ্বারা নির্মিত এক অভিনব চৌদোলে কামালকে বসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের মতো তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহু দূর হইতে সে রণতাণ্ডব নৃত্যের ও প্রবল ভেরিতূরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,''–
''ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,
কামাল! তু নেকামাল কিয়া ভাই !
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!'"
🍂

১৯২১ সালের শেষদিকে কবি রচিত কামালপাশা" একটি দেশাত্মবোধক কবিতা, যা সেই বীর সৈনিকের বীরত্ব, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং একই সাথে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে কামালপাশা চরিত্রটি বর্ণনা করেছেন। কামালপাশার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনির জয়গান:করে কবি অনবদ্য বর্ণনায় কাব্যের ছন্দে জগৎ কে বীররসে জাগাতে চাইলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্বপ্নের নায়ক কামাল তার অপরিসীম শক্তি ,সে বলশালী এবং তার বীরত্ব ও সাহসের বর্ণনা দিয়ে কবি উৎসাহিত করতে চেয়েছেন বঙ্গ জননীর সন্তানদের। কবির আন্তরিক চাওয়া ভীত শঙ্কিত দুর্বল বঙ্গযুবক দল কামালপাশার বীরত্বে উজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামে মেতে উঠুক ,দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে অগ্রণী হোক। ' তুর্কি জাতির সাহস: তুর্কিদের তেজোদীপ্ত লড়াই এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের অটল থাকার মানসিকতার চিত্র বিদ্রোহী কবি কে বিশেষ ভাবে প্রাণিত করেছিল। কামাল পাশা" কে কবি দেখেছেন ''তুরস্কের ত্রাতা" রূপে এবং তার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসায় তাঁর অনবদ্য কাব্যিক ছন্দে ,অসম সাহসী যোদ্ধার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। কামাল পাশার সংগ্রামের মাধ্যমে নজরুলের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী চেতনার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়।
স্বদেশ প্রেমিক কবি নজরুল কে রুশ বিপ্লব ও সংগ্রামী বীর সৈনিক কামালপাশার দেশভক্তি ও অজেয় বীরত্ব নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবির আদর্শ ছিল স্বপ্নের নায়ক প্রবল পরাক্রম শালী বীর কামালের মত যুবক বাংলার গৃহকোণ উজ্জ্বল করে ভরে উঠুক। ‘কামাল পাশা’ কবিতায় নজরুলের যে উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে তা আর তার অন্যকোনো কবিতায় এমন করে দেখা যায় না।
‘ সাব্বাস ভাই! সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।
পাঠিয়ে দিলি দুশ্মনে সব যমঘর একদম-সে রে!
বল্ দেখি ভাই, বল হাঁরে,
দুনিয়ায় কে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ার?’
এ সময় তুরস্কে মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতে ও খেলাফত আন্দোলন চলছিল। অসহযোগ আর খেলাফত আন্দোলনের দর্শনে নজরুল আস্থাশীল ছিলেন না। স্বদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জন আর মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের সালতানাত উচ্ছেদকারী নব্য তুর্কি আন্দোলনের প্রতি কবির সমর্থন থাকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন।সারাবিশ্বের শোষিতের মুক্তির সংগ্রামের সাথে নিজেকে একাত্ম ঘোষণা করে তিনি কামাল পাশার বিজয় কে সকল ঔপনিবেশিক বিরোধী লড়াইয়ের প্রস্তুতি মন্ত্র হিসাবে রূপ দিয়েছেন।
লেফট্রাইট লেফট্!! লেফট্রাইট লেফট!!
সাব্বাস ভাই! সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।/
পাঠিয়ে দিলি দুশ্মনে সব যমঘর একদম-সে রে!
কবিতাটি তে বাংলা শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের ও ব্যবহার করেছেন, এবং ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে সৈনিকের কুচকাওয়াজ যা একজন দুঃসাহসিক সৈনিক কবির পক্ষেই সম্ভব। তিনি ভেবেছিলেন, তুরস্কে যা সম্ভব, তা এখানেও সম্ভব। লাঙল ও গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ ও ‘সর্বহারা’ কবিতাগুচ্ছ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুবাদ ‘জাগ অনশন বন্দী ওঠ রে যত’ এবং ‘রেড ফ্লাগ’ অবলম্বনে রক্তপতাকার গান কে পেলাম তার প্রমাণ হিসেবে।সেই বছরের নভেম্বরে নজরুল আবার কুমিল্লায় গিয়েছিলেন এবং সে সময় ২১ নভেম্বর ভারতব্যাপী হরতাল ডাকা হয়েছিল। তিনি পথে নেমেছিলেন এবং অসহযোগ মিছিলের সঙ্গে শহর প্রদক্ষিণ করে গাইলেন-‘ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী।’ সে সময়ে ‘কামালপাশার সাথে তার আরো কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা রচিত হয়েছিল। ‘আনোয়ার ও ‘ভাঙার গান’ও এই সময়কার সৃষ্টি।
ঔপনিবেশিক শাসকেরা ধূমকেতুতে প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধ গদ্য বা অন্যান্য রচনার সম্ভার সহ্য করলেও ‘২২ সেপ্টেম্বরের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'আগমনী’ নামে ৮৯ পঙ্ক্তির দীর্ঘ কবিতাটি‘ একটুও কে সহ্য করতে পারলেন না। এতে নজরুল ইঙ্গিতে সমকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রকাশিত ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরোধী ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। গান্ধী, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার, পুলিনবিহারীসহ ছোট–বড় অনেক নেতার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বললেন জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে দেশমাতৃকার পূজায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র।
‘আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ।
এই দুলালাম বিজয়-নিশান, মরতে আছি-মরব শেষ।
প্রথম স্তবকটিতেই নজরুল তীব্র শ্লেষ ও ঈষৎ তির্যক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসু কণ্ঠের লেখনীতে :ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের বিপ্লব ও বিদ্রোহের ইঙ্গিত পেয়ে ধূমকেতুর ওই সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করে এবং রাজদ্রোহের ‘অপরাধ’এর কারণে কুমিল্লা থেকে নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে শুরু হলো তাঁর বিচার।
, ‘ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিবাদের ভাষায় কবিতায় লিখলেন---
‘আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী?
বিচারাধীন অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে নজরুল লিখলেন '' আত্মপক্ষীয় বয়ান ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’'। এই জবানবন্দী ব্রিটিশ ভারতে রাজবন্দীদের বিচারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সুইনহোর বিচারে নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু তাঁর জবানবন্দীতে দেশমুক্তির অপরাধে বিচারের নামে প্রহসনকে নজরুল যেভাবে কাঠগড়ায় তুলেছেন, ভারতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। তাঁর সুদীর্ঘ,বক্তব্যর কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ রাখলাম যা ১২ই মাঘ ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল।
‘''নজরুল বলেছিলেন আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে—রাজার মুকুট, আরধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আরজন সত্য, হাতে ন্যায় দণ্ড।'' আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়।.''..
''ভাঙার গান" ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কাজী নজরুল রচিত একটি বিখ্যাত কবিতা,এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন গবেষকের মতে , "ভাঙার গান" কবিতায় কবি নজরুল লোহার কপাট ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন, যা তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক ছিল। "ভাঙার গান"এ "কারার ঐ লৌহ কপাট"কবিতাটি বিপ্লবী কবির চেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। " কবিতাটির মূলভাব হলো অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করা। কবিতাটি তে কবি নজরুল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জনগণের মধ্যে জাগরণের ডাক দিয়েছেন।
কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট ,
রক্ত জমাট শিকল পুজোর পাষাণ -বেদী
ওরে ও তরুণ ঈষাণ
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ,
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি ॥
কবিতাটি র প্রতিটি পংক্তি আজও রক্তে দোলা দেয় , স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। BBC এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শোনাযায় ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কে বৃটিশ সরকার কারারুদ্ধ করলে তারই প্রতিবাদে স্ত্রী বাসন্তীদেবীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে নজরুল এই গানটি রচনা করেছিলেন। বাসন্তী দেবী তখন‘বাঙ্গলার কথা’ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।.এবং তখন ভাঙার গান’ শিরোনাম নিয়ে ‘ঐ পত্রিকায় ‘২০ জানুয়ারি ১৯২২’ সংখ্যায় এই গানটি প্রকাশিত হয়েছিল।
১৯২২ সালে প্রকাশিত এইসময়ের আরো একটি বিখ্যাত কবিতা"সাত-ইল-আরব" মূলত বীর রসাত্মক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা। এই কবিতায় কবি শাতিল আরব নদীর তীরে সংঘটিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং বীরদের আত্মত্যাগের বর্ণনা দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী কবি শাতিল আরব নদীর তীরকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যেখানে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও বীর যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য আত্মত্যাগ করেছে। এবং একই সময়ে প্রকাশিত আনোয়ার"কবিতাটিতে, এক বিপ্লবী সৈনিক জীবনের শেষ রাতের মর্মান্তিক পরিণতির প্রেক্ষাপট এঁকেছেন । পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ আনোয়ার,তার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও, দেশ ও স্বাধীনতার জন্য তার গভীর ভালোবাসার কথা স্মরণ করে। পরাধীনতার শিকল ভাঙতে এবং স্বাধীনতার জন্য আনোয়ারের দৃঢ় সংকল্প ও লড়াইয়ের মনোভাব সংবেদন শীলকবি গভীর ব্যথায় প্রকাশ করেছেন।
" বিপ্লবী সৈনিক আনোয়ারের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার জন্য তার অসীম আকাঙ্ক্ষায় জীবন কে উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত।পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে স্বাধীন মুক্ত জীবনের জন্য তার দৃঢ় সংকল্পের চিত্রটিই কবিতায় মূল বক্তব্য।পরাধীনতার এই বিভীষিকা থেকে মুক্তি চেয়েছিল আনোয়ার কিন্তু পরাজিত সৈনিক তার স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। এই কবিতাটি কবির বিপ্লবী চেতনার প্রতীক, যেখানে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।
মরমী কবির লেখনী থেকে এখানেও কিছু রচনার অংশ উপস্থাপিত করা হলো । ---,
'' চারিদিক নিস্তব্ধ নির্বাক। সেই মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রির পায়চারির বিশ্রী খটখট শব্দ। ওই জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দি। তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন – সমস্ত কিছুতে যেন একটা ব্যথিত-বিদ্রোহের তিক্ত ক্রন্দন ছল-ছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক বোধ হইতেছিল।সেইদিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।'
আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে মস্ত মস্ত লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার মাকে দেখিতেছিল। সহসা ‘মা’ বলিয়া চিৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিমানী-সিক্ত বায়ু হাহা স্বরে কাঁদিয়া গেল, ‘হায় মাতৃহারা!’
স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ রোষে নিজের বাম বাহু নিজে দংশন ক্রিয়া ক্ষত বখত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহ শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারেবারে নিপতিত হইয়া কারাগৃহ কাপাইয়া তুলিতেছিল এখন অস্ত্রগুরু আনোয়ার কে মনে পড়িল। তরুণবন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল ----
আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আপশোশ!
বখতেরই সাফ দোষ,
রক্তেরই নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙে গেছে শমশের – পড়ে আছে খাপ কোশ!

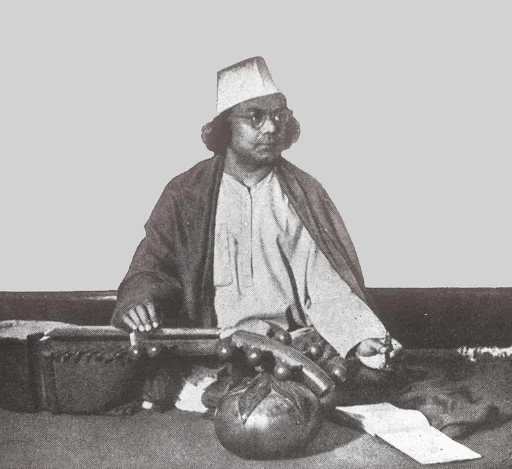













0 Comments