স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস: একটি দার্শনিক অনুসন্ধান
সত্যজিৎ পড়্যা
A Philosophical Inquiry into the Death Anniversary of Swami Vivekananda.
স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও ভারতীয় রেনেসাঁর অন্যতম পুরোধা। ৪ঠা জুলাই, ১৯০২—এই দিনেই তাঁর তিরোধান ঘটে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু কোনো সাধারণ ঘটনামাত্র নয়, বরং একটি গভীর দার্শনিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ আত্মযাত্রার পরিসমাপ্তি। এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের তিরোধানকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে—জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ, আত্মার চিরন্তনতা, কর্ম ও মুক্তির সম্পর্ক, এবং তাঁর ভাবনায় অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানচিন্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এটি উচ্চশিক্ষা স্তরে ভারতীয় দর্শন, জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিকতাসংক্রান্ত পাঠ্যচর্চায় নতুন আলো ফেলতে সক্ষম।
🍂

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান একটি চিরাচরিত মৃত্যু নয়। এটি ছিল এক সচেতন, গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন, পূর্বপ্রস্তুত চেতনার পরিণতি। তিনি বলেছিলেন:“I have given enough for fifteen hundred years. It is time to go back.”
এই ‘ফিরে যাওয়া’ কি কেবল পার্থিব দেহ ত্যাগ? নাকি তা ছিল এক পূর্ণবোধের মুক্তি—এক পরিপূর্ণ কর্মজীবনের শেষ বোধের দিকে যাত্রা?
স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের অনুসারী হলেও তিনি জীবনঘনিষ্ঠ ও কর্মমুখী দর্শনের প্রবক্তা। তাঁর মতে:মৃত্যু হচ্ছে না-বলিতে অন্তর নিহিত থাকা এক অন্যতর রূপান্তর।জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, আত্মার অনশ্বরতা ও কর্মফলের সূত্র তাঁর চেতনার কেন্দ্রে।তিনি লিখেছেন: “This life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others.”
এই ভাবনায় আমরা পাই—জীবন অর্থহীন নয়, মৃত্যুও নয় অন্তিম; বরং তারা উভয়েই বৃহৎ আত্মসাধনার কড়ি।
বেলুড় মঠে, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর তিরোধান ঘটে। আয়ুর মাত্র ৩৯ বছর হলেও তাঁর জীবনের গভীরতা অসীম।ভারতীয় দর্শনে ধ্যানমৃত্যু মানে মোক্ষসাধনার সফল পরিণতি। এই প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের মৃত্যু ছিল ‘সমাধি’—তাত্ত্বিক ‘সত্তা’র ব্রহ্মে লীন হওয়ার শেষ ধাপ।এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন ওঠে:
“জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধি কি মৃত্যু নয় বরং সচেতন আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ব লাভ?”তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সমাজ ও মানবতার জন্য নিবেদিত। কর্মযোগ তাঁর দর্শনের মূল স্তম্ভ।তাঁর মতে:“It is the duty of every person to work selflessly for the upliftment of mankind.”
এই দায়িত্ববোধ তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত চালিত করে। ফলে, তাঁর তিরোধান ছিল না কোনো ক্লান্তির পরিণতি, বরং সার্থক কর্মজীবনের পর এক শান্তিময় নির্বাণ।
এই কর্মতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন।
প্রতি বছর ৪ঠা জুলাই যেন একটি দার্শনিক অনুসন্ধানের দিন হয়ে ওঠে—আমরা নিজেদের আত্মপরিচয় নিয়ে ভাবি,প্রশ্ন করি—আমাদের জীবন কতটা সার্থক?
আমরা কি কেবল বেঁচে আছি, না কি সত্যিকার অর্থে জীবনযাপন করছি?তাঁর তিরোধান দিবস এই আত্মপাঠের দিন।
এই উপলক্ষ আমাদের স্মরণ করায়:“জন্ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, মৃত্যুও তেমনি এক জ্ঞানতপস্যার মাধ্যম হতে পারে।”
স্বামীজির চিন্তায় জন্ম ও মৃত্যু—এই দ্বৈততাকে ছাপিয়ে যায় ‘অদ্বৈত’ চেতনা।তিনি বিশ্বাস করতেন:আত্মা চিরন্তন, অবিনাশী দেহের ক্ষয় আত্মার ক্ষয় নয়,
সত্তার প্রকৃত গুণই হলো চেতনা, যা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিফলন।এই দৃষ্টিতে দেখা যায়—তাঁর তিরোধান ছিল এক মহাসিন্ধুপথে আত্মার যাত্রা।এই সাধনার মর্মার্থ হচ্ছে—“আমি”–র বিলুপ্তি নয়, বরং তা–ই মহা–“আমি”–র সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া।
স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান তাঁর দর্শনের সবচেয়ে নিখুঁত প্রকাশ।
তাঁর জীবনে যেমন কাজ ছিল, তেমনি ছিল ত্যাগ, জ্ঞান ও ভক্তির ভারসাম্য।
তাঁর মৃত্যু তাই এক নির্বাণ নয়—“জ্যোতির্ময় আত্মার অনন্ত আলোকমালার মধ্যে প্রবেশ”।তাঁর তিরোধান আমাদের শেখায়:
জীবন-মৃত্যু দুই-ই পথ


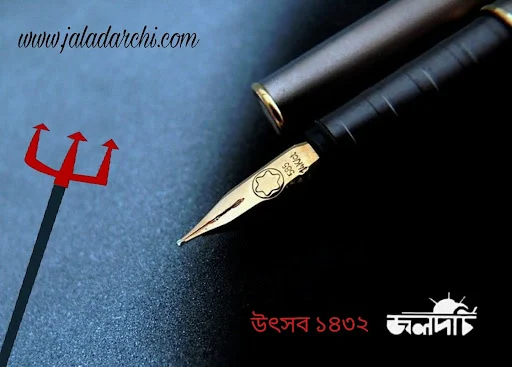












1 Comments
Fantastic 😍 লেখনী
ReplyDelete