দেবী প্রসাদ ত্রিপাঠী
প্রথম ভাগ - বৃন্দাবন পর্ব
দ্বাদশ পর্ব
এই দিন সকালে আর কোথাও বেরোলাম না। দুপুরে আশ্রমে ভোগ প্রসাদ খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে বিকেল চারটার সময় আমরা মথুরা-বৃন্দাবন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে রাধারমন মন্দিরে গিয়ে পৌছালাম। রাধারমন মন্দির থেকে দু পা এগিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দির। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের সহধর্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামাঙ্কিত এই মন্দিরটি বর্তমানে তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিগ্রহ স্থাপিত আছে। এখানে দর্শন ও প্রণাম করে আমরা ১০০ মিটার এগিয়ে শাহজি রাধারমন মন্দিরে গিয়ে পৌছালাম। শ্রী রাধারমনের অন্যত্র মন্দির ও বিগ্রহ আছে সেকথা আমরা পূর্বে বলেছি। সেই জন্য এই মন্দিরকে বলা হয় ছোট রাধারমন মন্দির।
আজ থেকে প্রায় একশ ষাট বছর পূর্বে লখনৌয়ের দুই শেঠজী শাহ কুন্দনলাল এবং শাহ ফুন্দনলাল এই রাধারমন মন্দিরের নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন এবং আট বৎসরের প্রচেষ্টায় এই মন্দির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৬৮ সালে। ১৮৭৬ সালে মন্দির জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মন্দিরের দেওয়ালে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতি কোথাও নেই পরিবর্তে মন্দিরের মেঝেতে তাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। স্থাপত্যকলার দিক দিয়ে এই মন্দিরটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বহন করে আছে। মুঘল, গ্রিক ও হিন্দু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নির্মিত এই মন্দির। মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ ঋতুরাজ ভবন বা বাসন্তী কামরা। বিভিন্ন রঙে কক্ষটির সিলিং এবং দেওয়ালগুলি চিত্রিত। বেলজিয়াম কাঁচের ওপরে সোনার জল ধরানো সিংহাসন ও দরজা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বসন্ত পঞ্চমী, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী ও গোবর্ধন পূজার দিনে এই কক্ষটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়বাতি ও সম্মুখস্থ বিশাল চত্বরের নীচে ফোয়ারাটিও অন্যতম আকর্ষণীয়। আমরা যেয়ে দেখলাম মন্দিরটি আলোকমালায় সজ্জিত। নাট মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে তখন নৃত্যগীতের আসর বসেছে এবং আবির খেলা হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ফুলে ফুলে সুশোভিত। আমরা যেয়ে প্রণাম করার পরে পূজারী আমাদেরকে আবীরে রাঙিয়ে দিলেন। মন্দিরটি আমাদের কাছে এতই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল যে এরপরেও দুদিন আমরা এই মন্দিরে এসে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এখান থেকে বেরিয়ে সেদিন আমরা ফিরে চললাম আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে। পরের দিনে আমাদের দুজনেরই শারীরিক অসুস্থতার জন্য সারা দিনে আর কোথাও বেরোতে পারিনি।

বৃন্দাবনের দোল
গোপিনীরা চলেছে যমুনায়। বসন্ত সমাগত। চারদিকে শ্যাম সবুজ তাল তমালের সারি। গাছে গাছে পাখির কূজন, ফুলে ফুলে ভরে গেছে পথ, কেউ যেন হলুদ চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। স্নান সেরে জল নিয়ে যাবে তাই গোপিনীদের মাথায় জলের কলস। চোখে মুখে তাদের খুশীর আমেজ। জনশূন্য পথের পাশে তুলসীর ঝোপ। সকলেই নিশ্চিন্ত মনে চলেছে। হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে কিশোর কানাহইয়া। কানাহইয়ার অত্যাচারে সকলেই অভ্যস্ত, কখন যে কি করে বসে তা কারোরই জানা নেই। কিন্তু আজ অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখছে ব্রজের দুলাল কৃষ্ণর হাতে রঙের পাত্র। কেউ কিছু বোঝার আগেই সেই পাত্র ছুঁড়ে দেয় গোপীদের দিকে। সামনেই ছিলেন শ্রী রাধিকা। সব রং যেয়ে পড়ে তার মুখে। মুহূর্তে শ্রী রাধিকার মুখ রাঙ্গা হয়ে যায়। দুহাত তুলে আনন্দে নেচে ওঠে কৃষ্ণ। অবশ্য এতে শ্রী রাধিকা বা গোপিনীরা কেউ রাগ করেনি। তারা যমুনার জল তুলে নিয়ে এসে পথের পাশে পড়ে থাকা পলাশ ফুল সেই জলে মিশিয়ে কানাহইয়ার দিকে ছুঁড়ে দেয়। অল্পক্ষণ পরেই জড়ো হয় কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতিরা। শুরু হয়ে যায় রঙের খেলা। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ আর তার সাথীরা অন্য পক্ষে শ্রী রাধিকা এবং গোপিনীরা। রঙে রঙে ভরে উঠে সেই জনশূন্য পথ। আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি রঙিন হয়ে ওঠে। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে কবির কল্পনায় নেমে এলো 'ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে। বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে।' শ্রীকৃষ্ণ আর গোপিনীদের এই রঙের খেলা শুরু হয়েছিল কবে তার সঠিক দিন তারিখ মাস বছর লেখা নেই। এই ইতিহাস লেখা আছে ভক্তজনের কল্পনায় কবির কবিতায় আর ব্রজবাসীর হৃদয়ে ও মানসলোকে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির সেই রঙ ধীরে ধীরে সীমানা ছাড়িয়ে সমস্ত ভারতভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্ম, বর্ণ, মত নির্বিশেষে আপামর ভারতবাসীর মধ্যে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন।
তবে বৃন্দাবনে হোলিখেলা প্রসঙ্গে পন্ডিতদের মধ্যে একটি মত প্রচলিত আছে যেখানে তারা বলেছেন মধ্য এশিয়া থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। এরা সকলেই ছিল যাযাবর শ্রেণীভুক্ত। কঠিন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হত। এদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল আভীর। গোচারণ ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। এরাই প্রথম বসতি স্থাপন করে মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল অঞ্চলে। একদিকে গরু, মহিষ পালনের জন্য অফুরন্ত গাছপালা, জীবন প্রতিপালনের জন্য যমুনার জল, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। স্বাভাবিকভাবেই যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী বসতি তারা গড়ে তুলেছিল। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির মিশ্রনে গড়ে উঠলো এক নতুন সংস্কৃতি। লেখা হলো নতুন কাব্য কাহিনী। অনেকের অভিমত কৃষ্ণ কাহিনীর বহু কিছুই এই আভীরদের রচনা এবং তারাই রঙ খেলার সূত্রপাত করে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে। যে সময়ে মাঠে মাঠে নতুন ফসল, গাছে গাছে ফুলের মেলা, পলাশের বনে আগুন লাগে। শুরু হয় প্রথম হোলি খেলা।
নন্দগাঁও, বর্ষানা, বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী আর রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধিকার কোমরে আবিরের পুটুলি বেঁধে দেওয়া হয়। তিনিই যেন ব্রজবাসীদের হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আবীর দিবেন। ব্রজমন্ডলে দোল উৎসব শুরু হয় বসন্ত পঞ্চমীর দিন বর্ষানার শ্রীজি মন্দিরে। এই মন্দিরের আরাধ্যা দেবী হলেন শ্রীরাধা। স্থানীয় লোকেরা বলেন লাডলীজীর মন্দির। কয়েকদিন আগে থেকে গোটা বর্ষানা গ্রাম জুড়ে শুরু হয়ে যায় উৎসবের প্রস্তুতি। মেয়েরা রঙিন পোশাকে সেজে উঠে। ঘরে ঘরে আসে আবির, গুলাল গোলাপ ফুলের পাপড়ি। প্রতীক্ষা কখন নন্দগাঁও থেকে আসবে গোপ বালকেরা। কতদিন আগে শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে গিয়েছেন গোপীদের কাছে। তাদের দই, দুধের হাঁড়ি ভেঙে অস্থির করে তুলেছিলেন। হোলির দিন গোপীরা তার মধুর প্রতিশোধ নেবে। একটু বেলা হলে ছেলের দল এসে হাজির হয়। তাদের পরনেও রংবেরঙের পোশাক। তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণ সাজে। বর্ষানার শ্রীজি মন্দিরের আঙ্গিনায় তখন হোলির গান শুরু হয়ে যায়। নন্দগাঁওয়ের পুরুষদের মাথায় পাগড়ি, হাতে ঢাল। মন্দিরের সামনে এসে তারা গান শুরু করে 'হোলি খেলনে আয়ি বর্ষণা, মোহন ঢোলে গলি গলি, মহলমে কিঁউ ছুপকে বৈইঠি, বাহারেন আজ বৃষভানু লালি'। অর্থাৎ বৃষভানু কন্যা রাধা প্রাসাদে কেন তুমি লুকিয়ে আছো। বেরিয়ে এসো আমরা রং খেলতে এসেছি। এবার তো সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। সখীদের নিয়ে বেরিয়ে আসে এই কালের রাধা। শুরু হয় আবির খেলা আর গান। নারী-পুরুষ, ছোট বড় কোন ভেদাভেদ নেই। সকলের আজ একটিই পরিচয় কৃষ্ণভক্ত ব্রজবাসী। মন্দির আঙিনা জুড়ে শুরু হয় লাঠমার হোলি খেলা। নন্দগাঁওয়ের পুরুষদের হাতে গোল গোল ঢাল, বর্ষাণার মেয়েদের হাতে লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি। আজ তারা গোপী। সারা বছর নন্দগাঁওয়ের ছেলেরা তাদের জ্বালাতন করে আজ তার শোধ নেওয়ার দিন। মেয়েরা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পুরুষেরা মাটিতে বসে পড়ে মাথার উপরে ঢাল নিয়ে। মেয়েরা হাতের লাঠি দিয়ে মারতে থাকে সেই ঢালের উপরে। শ্রীরাধার মন্দির থেকে হোলি ছড়িয়ে পড়ে বর্ষাণার গলিতে গলিতে।
পরবর্তী অংশ ত্রয়োদশ পর্বে

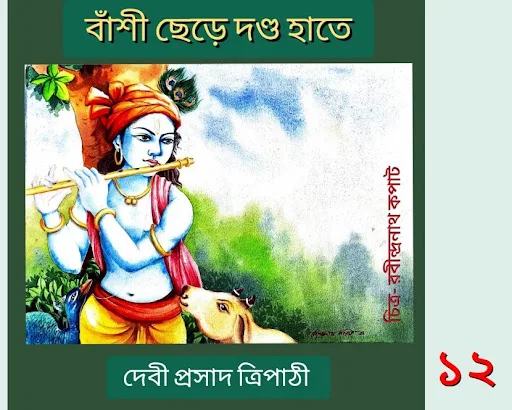












0 Comments